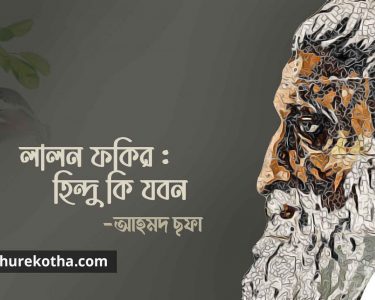-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
উভয় উদ্ধৃতিকে দীর্ঘতর করবার প্রলোভন সংবরণ করতে হয়; তবু এটুকু থেকেই আদিম মানুষের নাচে-ইন্দ্রজালে মেশা প্রাগ্বিভক্ত সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা মূলসূত্র আবিষ্কার করা যাবে।
প্রথম এ-সংস্কৃতি একের নয়, দশের; ব্যষ্টির নয়, গোষ্ঠীর। বিদগ্ধ ব্যক্তি বা বিদগ্ধ সমাজ বলে আলাদা কিছু নেই, সংস্কৃতি যতটুকু তাতে সকলেই সমান অংশীদার। দ্বিতীয়ত, এ-সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য প্রয়োগ, কর্ম, প্রকৃতিকে জয় করা। বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা বা অবসর বিনোদনের তাগিদ নয়, তাগিদ যেটুকু, সেটুকু কাজের তাগিদ।
প্রয়োগের খাতিরেই জ্ঞান, আবার জ্ঞানের দরুন প্রয়োগের উন্নতি-জ্ঞান আর কর্ম পৃথক হয়ে পড়েনি, জ্ঞান আর কর্মের প্রাগ বিভক্ত সমন্বয়। তৃতীয়ত, চেতনকারণবাদের দিকে, ধর্মের দিকে, ভাববাদের দিকে ঝোক নেই। ঝোকটা বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করবার দিকে, বহিঃপ্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে আবিষ্কার করবার দিকে, এক কথায় বস্তুবাদের দিকেই।
তাই বলে সচেতন জড়বাদের উপর ইন্দ্রজালের প্রতিষ্ঠা সত্যিই নয়; তা হবার কথাও নয়। আদিম অসভ্য মানুষ দল বেঁধে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করত, কিন্তু তখন তার সামর্থ্য অতি ক্ষীণ, তার সার্থকতা নেহাতই সংকীর্ণ। বৃষ্টির নাচ নাচলে সত্যিই এমন কিছু বৃষ্টি পড়ার বাস্তব সম্ভাবনা নেই, শিকারের নাচ নাচলেই এমন কিছু মৃগয়া সমাধা হবার কথা নয়।
আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ-শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।। একদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, অপর দিকে শূদ্র; একদিকে ইসাক-ফেয়ারোপুরোহিত, অপর দিকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত ক্রীতদাস; একদিকে শোষক-শাসকের দল, অপরদিকে শোষিত শ্রমিকের দল।
বাস্তব সাফল্যের সংকীর্ণতাকে কাল্পনিক সাফল্য দিয়ে পুরণ করা। ইন্দ্রজালের তাই অনেকখানিই ইচ্ছাপুরণ। তবুও তখন এই ইচ্ছাপূরণটুকুও জীবনসংগ্রামের অঙ্গ। এ ইচ্ছাপুরাণ বাস্তব সংগ্রামে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। অনেক মানুষ দল বেঁধে একসঙ্গে নাচছে। বৃষ্টির নাচ, কিংবা ভালুক শিকারের নাচ।
নাচছে আর ভাবছে, বৃষ্টিকে জয় করা গিয়েছে, জয় করা গিয়েছে শিকার। বৃষ্টি এবার পড়বেই পড়বে, শিকার এবার জুটবেই জুটবে। তারপর দল বেঁধে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া-মনের সামনে দুলছে কামনা সফল হবার ছবি, আর সেই ছবির কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণার ফসল জোগাড় করা, শিকার সমাধা করা অনেক বেশি সহজ!
এই প্রেরণাটুকু বাদ দিলে তখনকার ওই ভোঁতা হাতিয়ার হাতে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম অনেক দুরূহ হয়ে দাঁড়াত। তাই ইন্দ্রজাল তখন প্রকৃতিকে জয় করবার পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক বেশি করে, অনেক ভালো করে।
তারপর প্রকৃতির সঙ্গে দিনের পর দিন একটানা সংগ্রামের চেষ্টায় উন্নত হলো মানুষের হাতিয়ার, আর তাই উৎপাদনশক্তি। মানুষ উৎপাদনা করতে শিখল নিছক বেঁচে থাকবার জন্যে যেটুকু জিনিস দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস প্রকৃতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে, আর তখন থেকেই সম্ভব হলো অনেকের শ্রমের উপর নির্ভর করে কয়েক জনের পক্ষে শ্রমজীবনে অংশ গ্রহণ না করেও বেঁচে থাকা।
ফলে, সেই আদিম সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতি। শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ; সে সমাজে শ্রেণীবিভাগ, অতএব শ্রেণীসংগ্রামও। আর দেখা দিল ভাববাদ। ইন্দ্রজালের বদলে ধর্ম, আর ধর্মেরই সংস্কৃত সংস্করণ ভাববাদ। প্রয়োগের পরিবর্তে নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসার উৎসাহ। অব্যক্ত বস্তুবাদ বা জড়বাদের দিকে ঝোঁক ছেড়ে চেতনকারণবাদের বা ভাববাদের দিকে ঝোঁক।
শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি ভাববাদের উদয়। একে নিছক ঐতিহাসিক আপতন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে বদল করার মধ্যেও ভাববাদের চরম অসম্ভবের হাত থেকে প্রকৃত মুক্তি। একে রাজনৈতিক দল-বিশেষের প্রচারমাত্র বলে ব্যঙ্গ করাও অসম্ভব।
আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ-শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।। একদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, অপর দিকে শূদ্র; একদিকে ইসাক-ফেয়ারোপুরোহিত, অপর দিকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত ক্রীতদাস; একদিকে শোষক-শাসকের দল, অপরদিকে শোষিত শ্রমিকের দল।
রাজমিস্ত্রির কথা বলব? পরনের কাপড় বলতে তার কোমরে শুধু একটা নেংটি, কাজ করতে করতে তার আঙুলগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার যদি খিদে অসহ্য হয়, তাহলে নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
দল বেঁধে সবাই মিলে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা নয়-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ভার পড়ল শুধু একদল লোকের উপর; তারাই গতার খাটাবে, মাটি চাষবে, প্রাসাদ গড়বে, মন্দির গাথবে। শ্রমের ভার, কিন্তু শ্রমের ফলভোগের অধিকার নয়। সে-অধিকার অন্য শ্রেণীর, শাসক শ্রেণীর।
পরান্নজীবী এই যে নতুন শ্রেণীর মানুষ, এদের পক্ষে গতির খাটাবার তাগিদ নেই একটুও; তাই গতর খাটানোটা নেহাতই ইতরের লক্ষণ- “শূকর-যোনি, শ্বা-যোনি চণ্ডাল-যোনি বা” (ছন্দোগ্য উপনিষদ)। চণ্ডাল হলো শুয়োর আর কুকুরের সমগোত্র। গতির খাটাবার তাগিদ এতটুকুও নেই বলেই মাথা খাটাবার দেদার অবসর।
চিন্তা বা বুদ্ধি বা জ্ঞানবা যে কোনো নাম দিয়েই এই মাথা খাটানো ব্যাপারটাকে ব্যক্ত করা যাক না কেন-চরম উৎকর্ষ বলে ঘোষিত হলো।
এই জ্ঞান-এর উপর শাসক শ্রেণীর একেবারে একচেটিয়া অধিকার, কেননা শোষিত জনগণের উপর গতির খাটাবার ভার, এবং তখন হাতিয়ারের এমন উন্নতি হয়নি যে, জনগণ অল্পমাত্র গতির খাটিয়ে মানবসমাজের মোট অভাব দূর করে বাকি সময়টুকু সংস্কৃতির চর্চা করবে।
তাই যাদের উপর গতির খাটানোর দায়, মাথা খাটাবার মতো অবসর তাদের কাছে কল্পনার অতীত। প্রাচীন মিশরী প্যাপিরসে লেখা থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন হয়। তখন গতির খাটাবার দায়টা যে আজকের শ্রমিকের দায়ের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে :
কামারকে দেখেছি কামারশালে কাজ করতে। আগুনের মুখে হাপর নিয়ে সে দিনরাত বসে রয়েছে; ওইরকমভাবে একটানা বসে থাকতে থাকতে তার গায়ে পচা আর আঁশটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে, … ।
খোদাইকর সমস্ত দিন একটানাভাবে কঠিন পাথর কেটে চলেছে, তারপর দিনের শেষে হাত দুটো যখন তার নেহাতই চলতে আর চায় না, তখন হয়তো সারা দিনের মজুরি বাবদ দুমুঠে খাবার জুটল; কিন্তু পরের দিন সুর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে আবার কাজে না লাগে, তাহলে তার পিঠের দিকে হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে…।
রাজমিস্ত্রির কথা বলব? পরনের কাপড় বলতে তার কোমরে শুধু একটা নেংটি, কাজ করতে করতে তার আঙুলগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার যদি খিদে অসহ্য হয়, তাহলে নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
…হাঁটু দুটো বুকে দুমড়ে চেপে তাঁতি সমস্ত দিন ধরে তাঁত বুনছে, তাই সমস্ত দিন সে ঘরের মধ্যে বন্দি,-“সুর্যের আলো দেখবার জন্যে প্রাণটা যদি কখনও একান্ত ব্যাকুল হয়, তাহলে দোরের পাহারাদারকে নিজের রুটিটুকু ঘুষ না দিয়ে উপায় নেই।
… -মুচি যেন সারাটা দিন ধরে কাতরাচ্ছে, তার শরীর পচে গিয়ে পচা মাছের গন্ধ, আর যখন তার পেটের জ্বালা একেবারে অসহ্য হয়ে: ওঠে, তখন তার পক্ষে চামড়ায় দাত ফোটানো ছাড়া আর কোনো গতি নেই…
নীল নদের ধারে মানুষের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, এই তার অন্দর মহলের আসল চেহারা। কিন্তু শুধু মিশরই বা কেন? এর পাশাপাশি তুলনা করে দেখুন, আমাদের দেশে শ্রেণীসমাজে শূদ্র সম্বন্ধে মনোভাব “মানব” ধর্মে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে; তুলনা করলেই বোঝা যাবে, বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার খোলসগুলোয় যতই তফাত থাক না কেন, সে-সব খোলস ছাড়ালে সবগুলিরই চেহারা মোটামুটি এক :
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদা:।
-শূদ্রের জন্যে ছেঁড়া মাদুর, জীর্ণ বসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন।।
নোঙর ছবি সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো আধুনিক রাজনীতিকের কল্পিত প্রচার-পত্র নয়।
এ-হেন যে জনগণ, এদের পক্ষে মাথা খাটিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার কথা নিশ্চয়ই ওঠে না। ভগবান কী রকমের সুতো দিয়ে স্বৰ্গ থেকে পৃথিবীকে বুলিয়ে রেখেছেন? তিনি কেন সৃষ্টি করলেন মানুষকে, আর মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ ফেয়ারোকে? পশ্চিমের কোন পাহাড়ের পিছন দিকে মৃত আত্মার জমায়েত?
-এ সব প্রশ্ন জনগণের মাথায় ওঠে নি। মানুষকে এই জনগণ অমৃতের পুত্র বলে কল্পনা করবে। কেমন করে? কখন এরা বসে ভাববো : ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। ‘সোহং ব্রহ্ম’ বা ‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু’, কিংবা ওই ধরনের কোনো মহাবাক্যও এদের কারুর ঠোঁটে ফুটে ওঠবার কথা নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।
এই মেহনতের দায় ক্রীতদাসের উপর, শূদ্রদের উপর, ছোটলোকদের উপর। তাই এর মর্যাদা নেই। দিনের পর দিন মানুষ সভ্যতার কত আশ্চর্য চিহ্নই না গড়ে তুলতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার এত আশ্চর্য কীর্তির মূলে আসল অবদান যে মেহনন্তের, সেই কথাটা আর মনে রইল না।
প্রকৃতির সঙ্গে সমবেত সংগ্রাম নয়। আর। আসলে সংগ্রাম বেটুকু, সেটুকুর দায় লুষ্ঠিত শোষিত জনগণের উপর; জীবন তাদের কাছে বোঝামাত্র, চিন্তার জাল বোনা দূরে থাকুক, মরবার ফুরন্থতটুকুও তাদের যেন নেই। গতির খাটিয়ে শরীর ক্ষয় করার পথই যেন তাদের সামনে একমাত্র পথ।
আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় শোষকের দল। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার হাতিয়ার তখন যতই অনুন্নত আর স্থূল হোক না কেন, শোষণের পদ্ধতি এত নির্লজ আর অকুণ্ঠ যে, শোষকের ঘরে বিলাসের প্রাচুর্য। তাই তাদের কাছে প্রয়োগের তাগিদ, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের তাগিদ এতটুকুও নেই; নিছক চিন্তার জাল বোনাই সহজ আদর্শ।
যারা খেতি চষে, কাপড় বোনে, পাথর কাটে, প্রাসাদ গড়ে, তারা নেহাতই ছোটোলোকের দল; গতির খাটানোটা ইতরের লক্ষণ, মাথা খাটানোর মধ্যেই মানবাত্মার চরম উৎকর্ষ।
মিসমার হয়ে গেল মেহনতের মর্যাদা। কেননা, সভ্যতার যেটা সদর মহল, যেখানে মালিকদলের জমকালো দরবার, সেখানে আর মেহনতকারী মানুষের ঠাই রইল না। মালিকদের পক্ষে দায় নেই মেহনত করবার, গতর খাটাবার।
মাথা খাটিয়েই তারা ঠিক করে দেবে, কোনখানে কারা কেমনভাবে মেহনত করবে,-ফসল ফলাবে, কাপড় বুনবে, কাটবে। পাথর, গড়বে ইমারত। কিন্তু যে ক্রীতদাসের দল এই মেহনত করবে, তারা রইল চোখের আড়ালেই, পাইক-পেয়াদার চাবুক দিয়ে ঘেরা ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যে।
তাই শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর থেকে যে-মন দিয়ে, যে-বুদ্ধি দিয়ে মেহনতের পরিকল্পনা, সেই মনের সঙ্গে, সেই বুদ্ধির সঙ্গে মেহনতকারী হাতের সম্পর্ক গেল ঘুচে। রাজদরবারে বসে মিশরের রাজা আর সভাসদেরা মিলে হয়তো পরিকল্পনা করল, মরুভূমির বুকে পাথর দিয়ে গাথা হােক বিশাল, বিরাট, পিরামিড।
কিন্তু শুধু মাথা ঘামিয়ে এই পরিকল্পনাটুকু করেই তো সত্যিকারের পিরামিড গড়া হয় না। তার জন্যে আসলে দরকার লক্ষ মানুষের রক্ত-জাল-করা মেহনত, দীর্ঘ মেহনত। কিন্তু এই মেহনতটা সমাজের সদর মহলের আড়ালে, তাই চোখে পড়ে না।
এই মেহনতের দায় ক্রীতদাসের উপর, শূদ্রদের উপর, ছোটলোকদের উপর। তাই এর মর্যাদা নেই। দিনের পর দিন মানুষ সভ্যতার কত আশ্চর্য চিহ্নই না গড়ে তুলতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার এত আশ্চর্য কীর্তির মূলে আসল অবদান যে মেহনন্তের, সেই কথাটা আর মনে রইল না।
মানুষ মনে করল, এত সব কীর্তির আসল যে-গৌরব, তা হলো মানুষের মনের, বুদ্ধির, চেতনার। অথচ, চেতনা বা মন বা বুদ্ধি – সব কিছুই যে শেষ পর্যন্ত মানুষের মেহনতের কাছে ঋণী, এই কথাটুকু ভুলে গেল মানুষ।
কেননা, একমাত্র কাজের মানুষই মাটির পৃথিবীর মুখোমুখি। মেহনতের সময় যখন যুঝতে হয় পৃথিবীর সঙ্গে, তখন না বুঝে উপায় নেই, এই পৃথিবীটা কী নিৰ্ঘাত এক বাস্তব। লাঙল দিয়ে মাটি চাষবার সময় এ-প্রশ্ন আর মাথায় আসে না যে, লাঙলটা বাস্তবিকই সত্যি, না মনের একটা ভুল মাত্র, যেমন মনের ভুল হলো অন্ধকার জায়গায়দাঁড়িতে-দেখা সাপ।
মাথা খাটানো আর গতির খাটানো, পৃথিবীকে চেনা আর পৃথিবীকে বদল করা, কর্ম আর জ্ঞান – শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর থেকে যেন চিড় খেয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। যতদিন দল বেঁধে সমানে সমান হয়ে বাচ, ততদিন মেহনতের উলটো পিঠেই চেতনা, কর্মের উলটো পিঠেই জ্ঞান, দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বড় নিবিড়।
অবশ্যই একথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, তখন পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ার অনেক স্থূল, তাই মেহনতটাও নেহাতই অনুন্নত, পৃথিবীকে বদল করবার চেষ্টায় বাস্তব সাফল্য নেহাতই সংকীর্ণ। তাই তার উলটো পিঠে যে-চেতনা, সেই চেতনাও অনেকখানি স্থূল, অনেকখানিই ভ্ৰান্ত কল্পনা দিয়ে ভরা। তবু চেতনায় মেহনতে আত্মীয়তা, যে-আত্মীয়তা ঘুচল শ্রেণীসমাজ দেখা দেবার সময় থেকে।
যাকে আমরা দর্শনশাস্ত্র বলি, কিংবা আরো নিখুঁতভাবে বললে, যাকে বলা উচিত অধিবিদ্যা বা metaphysics, তার জন্ম-ইতিহাসের আসল রহস্যটা বুঝতে গেলে মূলসূত্র অনুসন্ধান করতে হবে এইখান থেকেই, সমাজের এই শ্রেণীবিভাগ থেকেই।
তার মানে এই নয় যে, সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হয়েছে অধিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের। এইভাবে বুঝতে যাওয়াটা যন্ত্রকে বুঝতে যাওয়ার মতো হবে-অর্থাৎ ভুল হবে। তার মানে, হঠাৎ কোনো এক মুহুর্তে ভূমিকম্প হওয়ার মতো সমাজ-জীবনে শ্রেণীবিভাগ ফুটে ওঠেনি।
আর কল টিপলেই যে-রকম জল পড়ে, সেইরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু জন্ম হয়নি। অধিবিদ্যার আর ভাববাদের। তবু একথাতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, যাকে আমরা দর্শনশাস্ত্র বা অধিবিদ্যা বলতে অভ্যস্ত, তার বীজ এই সামাজিক শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই; সে বীজ ফলে-ফুলে শোভিত।
হয়ে মহীরূহের রূপ নিতে ঐতিহাসিকভাবে অনেক দিন সময় নিয়েছিল নিশ্চয়ই! তবু, সামাজিক শ্রেণীবিভাগের কথাটা ভুলে গেলে দর্শনশাস্ত্রের আসল রহস্যটুকু বুঝতে পারা যাবে না। কেননা, এই অধিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের আসল কথা হলো, বিশ্বের আসল রহস্যকে জানতে চাওয়া-শুধু জানা, শুধু নির্মল, নির্লিপ্ত জ্ঞান।
অন্তত, দর্শনশাস্ত্রের যারা ডাকসাইটে পণ্ডিত, তারা মোটের উপর এই কথাটাই মেনে নিয়েছেন। দুনিয়া নিয়ে মাথা ঘামানো, বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে পরম সত্যের একটা বর্ণনা খোজা,-দুনিয়াকে বদল করবার কথা নয়।
মেহনত পড়ল চোখের আড়ালে, মেহনতের দাবিটা আর আসলে বড় দাবি হয়ে রইল না। সমাজের সদর মহলে শেষ পর্যন্ত চেতনার দাবিটাই চূড়ান্ত দাবি হয়ে দাঁড়াল। এ-চেতনা কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা, মেহনতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই,- আর মেহনতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলেই মাটির পৃথিবীর সঙ্গেও সম্পর্ক নেই!
কেননা, একমাত্র কাজের মানুষই মাটির পৃথিবীর মুখোমুখি। মেহনতের সময় যখন যুঝতে হয় পৃথিবীর সঙ্গে, তখন না বুঝে উপায় নেই, এই পৃথিবীটা কী নিৰ্ঘাত এক বাস্তব। লাঙল দিয়ে মাটি চাষবার সময় এ-প্রশ্ন আর মাথায় আসে না যে, লাঙলটা বাস্তবিকই সত্যি, না মনের একটা ভুল মাত্র, যেমন মনের ভুল হলো অন্ধকার জায়গায়দাঁড়িতে-দেখা সাপ।
এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করে ভৃগু তপস্যায় বসলেন, আর তপস্যা করে এসে বললেন; বাবা বুঝেছি, অন্নই হল ব্রহ্ম। কেননা অন্ন থেকেই এই সমস্ত উৎপন্ন, ইত্যাদি। বরুণ বললেন : হলো না। কেননা, এ যে নেহাতই স্থূল দৃষ্টির কথা। ভৃগু আবার তপস্যা করতে গেলেন, আর তারপর ফিরে এসে বলেন : বুঝেছি বাবা, অন্ন নয় প্রাণ।
মাথায় আসে না, খেতটা বাস্তব জিনিস কি-না, তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা। কাস্তে হাতে ফসল ফলাবার সময় এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে, কাস্তে আর ফসল দুই-ই হলো অবধারিত সত্য; কামারশালে হাতুড়ি পেটবার সময় টের পাওয়া যায়, হাতুড়ি আর লোহা দুই-ই কী রকম সত্যি জিনিস। কাজের মানুষ বাস্তব দুনিয়ার মুখোমুখি; তার যে চেতনা, সেই চেতনা এই বাস্তব দুনিয়ার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।
কিন্তু সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সময় থেকে মেহনতের দায় আর চেতনার দায়,-গতর খাটাবার দায় আর মাথা খাটাবার দায়- দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে গেল। যাদের উপর গতরা খাটাবার দায়, তাদের উপর শুধুই গতির খাটাবারই দায়; বাদের উপর মাথা খাটাবার দায়, তাদের উপর শুধুই মাথা খাটাবারই দায়। শুধু তাই নয়।
সামাজিকভাবে মেহনত থেকে বাদ পড়ল মর্যাদা। মেহনতকারীর দল হলো নেহাতই অস্পৃশ্য; ওদের মুখ দেখলে পাপ, ওদের ছায়া মাড়ালে পাপ। তাই যারা মাথা খাটায়, তাদের চোখের আড়ালে পড়তে চাইল। এই পৃথিবীটা, যে পৃথিবীর সঙ্গে অস্পৃশ্য মেহনতকারীদের অমন নাড়ির সম্পর্ক।
ওরা মশগুল হয়ে উঠল শুধু চেতনাকে নিয়ে-সে-চেতনা বুঝি বাস্তব দুনিয়ার চেতনা নয়-নিছক চেতনা, স্বাধিকারপ্রমত্ত স্বয়ত্ত্ব, সর্বশক্তিমান। ফলে এই বিশুদ্ধ চেতনাটাই হয়ে দাঁড়াল আসল সত্য, চরম সত্য। চেতনার দাবিই হলো চরম দাবি, যে জিনিস চেতনার দাবি চোকাতে পারবে না, সে-জিনিস সত্যি হতে পারে না।
এ-কথা অবশ্যই শাসকরাও বুঝেছিল যে, অন্নের উৎপাদন না হলে শেষ পর্যন্ত কিছুই টেকে না; কিন্তু তাই বলে অন্নের এই উৎপাদনকেই ধ্রুব আদর্শ বলে মনে করা নেহাতই স্থূল দৃষ্টির পরিচয়! উপনিষদের ভৃগুবরণ সংবাদ-এ এই মনোবৃত্তিরই স্বাক্ষর। বরুণের ছেলে ভূগু-র ইচ্ছে হলো সবচেয়ে চরম সত্যকে জানিবার, তাই বাবার কাছে গিয়ে ভূণ্ড বললেন : ব্রহ্ম কী, সে-বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।
বরুণ বললেন : ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা বর্ণনা শুনলেই ব্রহ্মকে তুমি যে জানতে পারবে, এমন আশা নেই; তুমি তপস্যা করো, তপস্যা করলেই ব্রহ্মকে জানতে পারবে। (‘তপস্যা’ -দৈনন্দিন প্রয়োগ থেকে অনেক দূরের কথা, বিশুদ্ধ চেতনায় আশ্রয় নেবার কথাই)। তবে একটা মূলসূত্র পেলে তপস্যা করবার সুবিধে হয়।
বরুণ তাই মূলসূত্র হিসেবে ছেলেকে বলে দিলেন- ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যার থেকে এই সমস্ত জিনিস জন্মেছে, জন্মাবার পর যার উপর নির্ভর করেছে এবং শেষ পর্যন্ত যার মধ্যেই তা বিলীন হয়ে যাবে, তাই হলো ব্রহ্ম।
এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করে ভৃগু তপস্যায় বসলেন, আর তপস্যা করে এসে বললেন; বাবা বুঝেছি, অন্নই হল ব্রহ্ম। কেননা অন্ন থেকেই এই সমস্ত উৎপন্ন, ইত্যাদি। বরুণ বললেন : হলো না। কেননা, এ যে নেহাতই স্থূল দৃষ্টির কথা। ভৃগু আবার তপস্যা করতে গেলেন, আর তারপর ফিরে এসে বলেন : বুঝেছি বাবা, অন্ন নয় প্রাণ।
বরুণ বললেন- হলো না, আবার তপস্যা করো। তৃতীয়বারের তপস্যায় ভূণ্ড বললেন : মনই হলো ব্রহ্ম। চতুর্থবারের তপস্যায় তার মনে হলো : বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কিন্তু বরুণ, বললেন; এখনো হয় নি, আরো তপস্যা করতে হবে।
অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ইন্দ্রজাল ছেড়ে মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে এক ধাপে বিশুদ্ধ দার্শনিক ভাববাদে পৌঁছোয়নি; ইন্দ্রজালের পর ধর্ম, ধর্মেরই বিদগ্ধতম সংস্করণ ভাববাদ। যতদিন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, ততদিনই এই কথা, -ঘুরে ফিরে নানানভাবে নানান পথ দিয়ে যুগে যুগে ভাববাদেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি।
শেষবার চরম তপস্যা করে ভৃগু বুঝতে পারলেন, আসলে অন্ন নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়, -আনন্দই হল ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই সব কিছুর জন্ম, ইত্যাদি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক-শ্রেণীর ভঙ্গি এই উপাখ্যানের ব্যঞ্জনা হয়ে রয়েছে। শুরুতে অন্ন, অন্ন না হলে সমাজের ভিতই যে গাথা হয় না।
কিন্তু তাই বলে অন্নকে চরম সত্য হিসেবে স্বীকার করা নেহাতই ছোটলোকমির পরিচয়! স্থূলদুষ্টর অল্পবুদ্ধি মানুষ অন্নকে স্বীকার করুক, নুয়ে পড়ুক অন্ন উৎপাদনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। অবশ্যই, শুধু অন্ন উৎপাদনের দায়িত্বই, শুধু কর্মের দায়িত্বই; তাই বলে কর্মফলে অধিকার তো নয়।
যারা উচ্চস্তরের মানুষ, কর্মফলের অধিকার তাদের বলেই কর্মজীবনের দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। তাই তারা ওই ছোটলোকদের মতো অন্ন উৎপাদনের দায় নেবে কেন? তারা এগিয়ে চলুক ধাপে ধাপে অধ্যাত্ম সত্য আবিষ্কারের পথে। ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর সত্যের আবিস্কার-শেষ ধাপে আনন্দ, শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্যের আনন্দ, আনন্দই ব্রহ্ম।
সমাজের এক-প্রান্তে একদল নির্বোধ মানুষ। শুধু অন্নের উৎপাদনে নিজেদের শরীর-মন ক্ষয় করে ফেলুক। সমাজের আর-এক-প্রান্তে বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ চিন্তায় মগ্ন আর একদল মানুষ সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারই তাদের জীবনে পরম পুরুষার্থ হয়ে থাকুক, আধ্যাত্মিক চেতনার চরমে পৌঁছে তারা হৃদয়ঙ্গম করুক, আনন্দই ব্রহ্ম। বিশুদ্ধ আনন্দই হলো বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠি।
তাই মার্কস বলেছেন : আধ্যাত্মিক কাজ আর বাস্তব কাজ, এই দুয়ের মধ্যে বিভাগ দেখা দেবার আগে পর্যন্ত শ্রমবিভাগ প্রকৃত বিভাগে পরিণত হয়নি। সেই সময় থেকে মনে হতে পারে যে, চেতনাটা বাস্তব জগতের চেতনা ছাড়া বুঝি অন্য কিছু।
চেতনা যখন থেকে সত্যিই এমন একটা কিছুকে বোঝাতে চায়, যা বাস্তব কিছু নয়, তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই সর্ব-সম্পর্ক বিরহিত হয়ে এই চেতনা বিশুদ্ধ মতবাদ, ঈশ্বরতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে একটা ধর্মমত-জাতীয় কিছুতে পরিণত হয়।
অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ইন্দ্রজাল ছেড়ে মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে এক ধাপে বিশুদ্ধ দার্শনিক ভাববাদে পৌঁছোয়নি; ইন্দ্রজালের পর ধর্ম, ধর্মেরই বিদগ্ধতম সংস্করণ ভাববাদ। যতদিন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, ততদিনই এই কথা, -ঘুরে ফিরে নানানভাবে নানান পথ দিয়ে যুগে যুগে ভাববাদেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি।
তাই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্ছেদের মধ্যেই ভাববাদ খণ্ডনের মূলসূত্র। তাই মার্কস বলছেন : এতদিন ধরে দার্শনিকেরা নানানভাবে দুনিয়াকে শুধু ব্যাখ্যা করবারই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো একে বদল করা!
(সমাপ্ত)
…………………….
ভাববাদ খণ্ডন – মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
……………………………….
ভাববাদ-আধ্যাত্মবাদ-সাধুগুরু নিয়ে লিখুন ভবঘুরেকথা.কম-এ
লেখা পাঠিয়ে দিন- voboghurekotha@gmail.com
……………………………….
………………….
আরও পড়ুন-
ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই : এক
ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই : দুই
বুদ্ধি দিয়ে, তর্ক করে, ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না : প্রথম পর্ব
বুদ্ধি দিয়ে, তর্ক করে, ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না : দ্বিতীয় পর্ব
ভাববাদকে খণ্ডন করা যায়নি : পর্ব এক
ভাববাদকে খণ্ডন করা যায়নি : পর্ব দুই
ধর্ম আর ভাববাদ