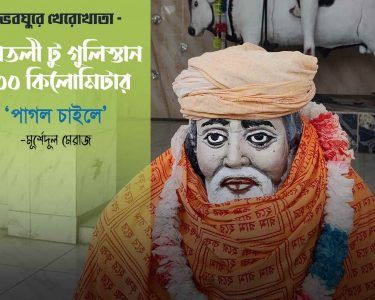-মূর্শেদূল কাইয়ুম মেরাজ
এই তো সেদিনের কথা। ঢাকা শহরের শিকারীরা লোক-লশকর, তীর-বর্শা, বন্দুক নিয়ে হাতি বা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়তো শিকারে। বজরায় চেপে শিকারে যাওয়ার ইতিহাসও বেশি পুরানো না। স্থানীয় জমিদারদের এই সখ এড়িয়ে যেতে পারেনি সুলতানী, এরপর মোগল শাসকরাও। ইংরেজ আমলে তো কথাই নেই। সাহেবদের এই সখের তাওয়ায় ঘি দিতে এগিয়ে এসেছিল শহরের ধনাঢ্যরা। খেতার পাওয়ার আশায় অনেকেই সাহেবদের জন্য শিকারের সঙ্গে রাখতো আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। শিকার করতে ঢাকা ছেড়ে বেশি দূরে যেতে হতো না। শহরে আশপাশেই ছিল শিকারের অভয়ারণ্য। বাঘ, হরিণ, বন্য শুকরসহ আর নানা জাতের পাখি শিকার করে ফিরতো তারা। ইংরেজ আমলে শিকার করা বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। সমালোচকরা বলে জমিদারদের লোক প্রস্তুত থাকতো সবসময়। কোনো সাধারণ শিকারীর হাতে বড় আকারের বাঘ মারা পড়লে তারা জমিদারদের কানে খবর তুলে দিতো। পেতো বাড়তি বকশিশ। জমিদাররা গোপনে সেই মৃত বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে সদর্পে ছবি তুলতো। তারপর সেই ছবি বাঁধাই করে লাগিয়ে রাখতো বৈঠকখানার দেয়ালে। দুপাশে দোনলা বন্দুক। সবাইকে গর্ভ ভরে শোনাতো বাঘ শিকারের ফাদা গল্প। কয়েক দশক আগেও ঢাকার চারপাশ জুড়ে ছিল জঙ্গল-ঝোপঝাড়। এরমধ্যে জয়দেবপুরের শালবন ছিল শিকারীদের অন্যতম পছন্দ। জানা যায়, ঢাকাকে মোগল রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দানকারী মোগল সুবেদার ইসলাম খান ১৬১৩ সালে ভাওয়ালের জঙ্গলে শিকার করতে যেয়ে মারা যান।
এই সব আগুন্তুক শিকারীদের নিশানায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে বনের প্রাণীকূল। আর বাকিটা করেছে প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা কাঠ চোররা। জয়দেবপুরের জঙ্গলই আজকের গাজীপুর। বন নেই। আছে বনায়ন। লোক দেখানো রাস্তা ঘেঁষে কয়েকটা গাছ! তারপর শুধুই শূন্যতা। জঙ্গল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিস্তৃত খোলা মাঠের ফাঁকে ফাঁকে খুব গুছিয়ে লাগানো গোটা কয়েক গাছ, তারপর আবার খোলা মাঠ। এটাইকেই মানচিত্রে দেখানো হয় জঙলা এলাকা হিসেবে।
জঙ্গল নেই তাই জন্তু-জানোয়ার থাকার প্রশ্নই আসে না। বনায়নের ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠেছে বসতি। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই সব বসতির বয়স বেশিদিনের নয়। তবে এই জঙ্গলে কয়েক শতক ধরে বাস করে আসছে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী কোচ। গাজীপুর ছাড়াও টাঙ্গাইল, মধুপুর, ময়মনসিংহ ও শেরপুরে কোচ আদিবাসীদের দেখা যায়। জানা যায়, ভাওয়ালের রাজা একবার বোকা মানুষ দেখার ইচ্ছা পোষন করলে তার অনুগতরা বোকা মানুষ খুঁজতে বের হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা বিহার থেকে কোচদের নিয়ে আসে। ভাওয়ালের রাজা কোচদের দেখে ভীষণ খুশি হন। খাজনা দিতে হবে এই শর্তে জমি দেন বসবাস ও চাষাবাদের জন্য। কিন্তু কোচদের অনেকেই বুঝতে পারে না নিজে চাষাবাদ করে রাজাকে কেন তার ভাগ দিতে হবে। কোচদের অনেকেই রাজার দেয়া জমি ছেড়ে গাজীপুর জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে গাছের ফল ও শিকার করে দিন কাটাতে থাকে। কোচরা জঙ্গল নষ্ট করছে এমন কথা রাজার কানে পৌঁছালে সৈন্যদের নির্দেশ দেন কোচদের ধরে আনার। সৈন্যরা জঙ্গলে প্রবেশ করেই প্রথম যে কোচকে দেখতে পায় তাকেই ধরে আনে। কোচরা জঙ্গলে বসবাস করছে এই সত্যতা স্বীকার করে নিলে ধৃত কোচকে রাজা ফাঁসির হুকুম দেয়। রাজা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেও ধৃত কোচ ব্যক্তি জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে কোচ ব্যক্তি বলে ওঠে ‘রাজা ও রাজা তুই বলে ফাঁসি দিবি, তো তাড়াতাড়ি দিয়ে দে, গরু চড়াতে দিয়ে আসছি ওগুলোকে গোয়ালে নিতে হবে। এই কথা শুনে রাজা হেসে শেষ। বোকামি দেখে রাজা ধৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এর ঐতিহাসিক ভিত্তি যাই হোক গাজীপুরের জঙ্গলে বসবাসের ইতিহাস বলতে কোচরা এ কথাগুলোরই বলে থাকে।
নিজেদেরকে উচ্চবংশীয় ক্ষয়িত্র বলে দাবী করলেও কোচরা তাদের আদি ইতিহাসের প্রায় সবটাই ভুলতে বসেছে। জোড়া তালি দেয়া যে কাহিনীটা জানা যায় তা অনেকটা এরকম- রাজা পরশুরামের সময় চীনের কোনো অঞ্চল থেকে তিব্বত হয়ে একটি সম্পদশালী সম্প্রদায় ভারতে আসে। তারা নিজেদের উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবী করতো। তাদের বসতির এলাকায় প্রবেশের জন্যও নিতে হতো অনুমতি। তাদের উঠানে কেউ পা দিলে সে স্থানটি তারা নতুন করে লেপে দিতো। অন্য সম্প্রদায়ের লোকে কোনো কিছু স্পর্শ করলে তা ফেলে দিতো। রাজা পরশুরামের কানে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি এই ক্ষত্রিয়দের উপর ক্ষিপ্র হয়ে ওঠেন। ঘোষণা করেন ক্ষত্রিয় নিধনের। তার নির্দেশে সৈন্যদল তলোয়ারের আঘাতে কাটতে শুরু করে ক্ষত্রিয়দের মাথা। এই ক্ষত্রিয়রা পরশুরামের বাহিনীর কাছে ক্রমশ অসহায় হয়ে ওঠে। দিশেহারা হয়ে তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিকবিদিক পালাতে শুরু করে। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি কারো। শুধু মায়া বসতঃ জনৈক্য সৈন্য এক প্রসুতি নারী ও তার বোনকে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়। ঐ দুই নারী বিহারের ঋষি বিশ্বামিত্রার স্বরণাপন্ন হয়। সবকথা শুনে বিশ্বামিত্রা বিহারের জঙ্গলে অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে বসবাসের অনুমতি দেন। তবে পরশুরামের বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তাদের বনের আদিবাসীদের ভাষা ও আচার-আচরণ শিখে নেয়ার উপদেশ দেন। শতর্ক করে দেন কোনোভাবেই প্রচার না হয় তারা উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়। জীবন বাঁচাতে বিশ্বমিত্রার কথা মেনে ক্ষত্রিয়রা জঙ্গলে যেয়ে বসতি গড়ে তোলে। পোশাক ছেড়ে তারা মিশে যায় জঙ্গলে। কাঁচা খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকে। তাদের সংবাদ পরশুরামের কানে পৌঁছালে তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণ করেন বিহারের জঙ্গলে। সৈন্যরা জঙ্গলে কোচদের মতো দেখতে দুজন নারীকে খুঁজে বের করলেও তাদের ভাষা তারা বুঝতে না পেরে তাদের আদিবাসী ভেবে ফিরে যায়। এভাবে সংকোচিত হয়ে থাকার ফলে তারা পরিচিতি পায় সংকোচ বা কোচ নামে। সেসময়কার কোচদের ভাষার নাম ছিল থারগেরোফা মিথিলা। কোচরা মনে করে জঙ্গলে বসবাসের সময় দেবতা বুড়াবুড়ি তাদের রক্ষা করে। এই বুড়াবুড়িকে তারা বলে বোদাইবুচি। বছরে একবার তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বোদাইবুচির পুঁজা করে। এই পুঁজা গেথেনচাওয়া, গ্রাম পুঁজা, সনাতন গোসাই পুঁজা, লেবা পুঁজা, বনোদুর্গা পুঁজা নামেও পরিচিত। ৫ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেলো কোচদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুড়াবুড়ির নাচ। সমতলের আদিবাসী কোচ সম্প্রদায়ের অনেক কিছু হারিয়ে এই আনুষ্ঠানিকতাটাই শুধু টিকে আছে। এই পুঁজায় সবকিছুই কাঁচা খাওয়ার নিয়ম। পুঁজার জন্য কাঁচা মাছ না ধুয়ে, চালের গুড়ার সঙ্গে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ ও আদা দিয়ে তেল ছাড়া রান্না করা খাবারের নাম লেবা। একই প্রকৃয়ায় প্রস্তুত করা খাবার আগুনে পুড়িয়ে বড়া বা পিঠা প্রস্তুতকে কোচরা বলে পুসরা পিত্তা। পুঁজার সপ্তাহ খানেক আগে শনি বা মঙ্গলবারে আতপ চাল দিয়ে রান্না করা হয় কাঁচা মদ। গ্রামের প্রধাইন্না বা বয়োজ্যোষ্ঠরা এই আতপ চাল দান করে। যারা রান্না করবে তারা সারাদিন উপবাস করে এই আতপ চাল ঢেকিতে ভেঙে মদ রান্না শুরু করে। রান্না শেষে দেবতাকে উৎসর্গ করে তারা উপবাস ভাঙে। আর যে বাড়িতে রান্নার আয়োজন হয় সেই বাড়ি থেকে পুঁজার আগ পর্যন্ত ভিক্ষা দেয়া বন্ধ থাকে।
এই উৎসবটি ছাড়াও তারা সাকরাইনের সময় হয় বাস্তু বা মাটি পুঁজা, বৈশাখ মাসে হয় চরখ পুঁজা নাই নাই করে কোনোমতে করে। তবে কোনো অনুষ্ঠানেই আর পূর্বের জৌলুস এখন আর নেই। বোকাসোকা কোচদের কাছ থেকে তাদের জমিজমা ক্ষমতাশালীদের কাছে চলে গেছে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের কাছ থেকে এই জমিজমা কাগজপত্রে লিখে নিয়েছে প্রভাবশালীরা।
পুঁজার দিন কোচরা মাটির একটি বেদি বানায়। তারা বিশ্বাস করে, মহাসমুদ্রের উপর আছে এক কচ্ছপ। তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ভূমি। তাই কচ্ছপ তাদের কাছে পূঁজনীয়। আদিতে তারা কচ্ছপের রক্ত দিয়ে পূঁজা করতো। পরে তারা ভেবে দেখলো কচ্ছপ এতো কষ্ট করে নিজ পিঠে করে ভূমি পানির উপর তুলে রেখেছে তাকে বদ করা ঠিক না। তাই পরে তারা মাটি দিয়ে কচ্ছপের পিঠের মতো ঢিবি বানিয়ে পুঁজা করতে শুরু করে। এই মাটির ঢিবির উপর কেন্দু বা কুটিশ্বর গাছের ডাল চেছে চটি বানিয়ে বামদিকে ৪টি আর ডানদিকে ৩টি কাঠি বসায়। বামদিকেরটি বুড়া আর ডানদিকেরটি বুড়ির প্রতীমা। প্রতিটি কাঠিই গুড়ি সুতা দিয়ে আড়াআড়ি বাঁধা হয়। বুড়াবুড়ি বোঝাতে কাঠিগুলোর মাথায় লাগানো হয় তুলা। পুঁজার সময় এই তুলায় লাগানো হয় সিন্দুর। মাটির ঢিবির চারপাশে কেন্দু পাতার উপর লেবা দিয়ে তার উপর রাখা হয় ৭টি ডিম। পুঁজা শুরুতে দুটি মুরগি জবাই করে কাঁচা রক্ত মাটির ঢিবির চারপাশে ছিটিয়ে মন্ত্র পড়া হয়। বুড়াবুড়িকে উৎসর্গ করা হয় এই কাঁচা রক্ত। তারপর শুরু হয় মন্ত্র। পুঁজা শেষে আতপ চালের কাচা মদ খেয়ে তবে শুরু হয় উৎসব। একপাশে প্রসাদের জন্য বানানো হয় লেবা। আর অন্যপাশে বুড়াবুড়িকে উৎসর্গ করা মুরগি, পুঁজার ডিম পোড়ানো হয়। বয়োজ্যোষ্ঠরা গোল হয়ে বসে মুরগি-ডিমের ভাজা দিয়ে মদ খায়। আর অন্য সবাইকে দেয়া হয় প্রসাদ। শাল পাতার উপর লেবা নিয়ে গোল হয়ে বসে সকলে মিলে খায়। এই টুকু আনুষ্ঠানিকাতই টিকে আছে গাজীপুরের কোচদের মধ্যে। এই উৎসবটি ছাড়াও তারা সাকরাইনের সময় হয় বাস্তু বা মাটি পুঁজা, বৈশাখ মাসে হয় চরখ পুঁজা নাই নাই করে কোনোমতে করে। তবে কোনো অনুষ্ঠানেই আর পূর্বের জৌলুস এখন আর নেই। বোকাসোকা কোচদের কাছ থেকে তাদের জমিজমা ক্ষমতাশালীদের কাছে চলে গেছে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের কাছ থেকে এই জমিজমা কাগজপত্রে লিখে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। জঙ্গলে বসবাস করলেও জঙ্গলে জমি বিক্রি করার ক্ষমতা ছিল না তাদের। কিন্তু জমির দালালরা তাদের নামের পেছনে সরকার, বর্মণ, চৌধুরী, রাই ইত্যাদি পদবী লাগিয়ে এসব জমি হস্তগত করেছে। তাই অনেক কোচই আজ বাস্তু হারা।
মাটির ঘরে থাকে কোচরা। উপরে টিন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মাটির ঘরের মতোই সাদামাটা তাদের ঘরবাড়ি। তাদের ঘর অনেকটা মিলে গারো ও টিপরাদের সঙ্গে। সময়ের বিবর্তণে এখন তাদের ঘরে বিশেষত কিছু নেই। আসবাবপত্রও সব আধুনিক। পোশাকের বেলাতেও তাই। জানা যায়, একসময় কোচ পুরুষরা পরতো লেংটি। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় পরতো ছোট ধুতি, শাল আর মাথায় দিতো পাগড়ি। বেশিভাগ কাঠের খড়ম পরলেও সমাজের সম্মানিত বয়োজ্যোষ্ঠরা তাল গাছের বাকল ও পাট দিয়ে বিশেষ ধরনের জুতা পরতো। এই জুতার নাম ছিল পুকফুতি। আর নারীরা কোমরে জড়াতো এক খণ্ড ছোট কাপড়। এই কাপড়ের এক অংশ আঁচলের মতো সামনের দিক দিয়ে উঠে পিঠ হয়ে আবার কোমড়ে যেয়ে মিশতো।
কোথাও চাকরি করতে গেলে তাদের অন্যদের থেকে বেতন দেয়া হয় কম। নানা প্রতিবন্ধকতায় কোচদের অনেকেই জড়িয়ে যাচ্ছে নানা অপরাধের সঙ্গে। এছাড়াও নানা সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের আক্রমণের শিকার হতে হয় তাদের।
কোচদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও বেশিভাগ সময় তারা বাংলাতেই কথা বলে। লেখাপড়া যতটা করার তাও চলে বাংলাতেই। বর্তমান প্রজন্মের বেশিভাই কোচই বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্থ। অনেকেই তাদের নিজের ভাষা বলতে পারে না। অস্থির সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে কোচরা হারিয়েছে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য। প্রতিকূল পরিবেশ ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির অসহযোগীতায় তারা অনেকে নিজেদের কোচ হিসেবে পরিচয়ও দিতে চায় না। নানা প্রতিবন্ধকতায় শিক্ষায়ও তারা খুব একটা এগুতে পারেনি। একসময় বনের হরিণ, শুকর, খরগোস শিকার ও বনের জমিতে আলু চাষ করে জীবন ধারণ করলেও এখন আর সে সব নেই। বেশিভাগ কোচই এখন দিনমজুরের কাজ করে। কোথাও চাকরি করতে গেলে তাদের অন্যদের থেকে বেতন দেয়া হয় কম। নানা প্রতিবন্ধকতায় কোচদের অনেকেই জড়িয়ে যাচ্ছে নানা অপরাধের সঙ্গে। এছাড়াও নানা সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের আক্রমণের শিকার হতে হয় তাদের।
বাংলাদেশের আর সবার মতোই অধিকারের সঙ্গে বাঁচতে চায় কোচরা। চায় অধিকার নিয়ে বাঁচতে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাদেরকে যেন অবহেলা না করা হয় এই আকুতি প্রত্যেক কোচের। তারপরও জঙ্গলে রাত নামে, ভোরে সূর্য উঠে বদলায় না কোচদের ভাগ্য। শুধু পাল্টে যায় সময়ের কাঁটা। কোচদের দারিদ্রতা আরো বাড়ে। একবেলা খাবারের জোগার হলে অন্য বেলা চুলা জ্বলে না। তারপরও অধিকার আদায়ের জন্য নতুন নতুন গান বাঁধে তারা। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন কোচরা পাল্টাচ্ছে ধর্ম। কেউ হয় মসুলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বা খ্রিস্টান। কিন্তু মনে মনে প্রত্যেকেই থেকে যায় কোচ। শত শত বছর আগে যারা এসেছিল এই ভূমিতে। এই মাটির পুঁজা করে তারা। এই ভূমির গাছের পুঁজা করে তারা। তারপরও যদি বলা হয় তারা বাংলাদেশী নয় তবে কষ্ট তো হবেই। এই কষ্ট বিস্ফোরনে রূপ নেয়ার আগেই মমতা আর ভালবেসে তাদেরকে সকলের সঙ্গে এক সাঁড়িতে জায়গা করে দিলে জাতি হিসেবে আমরাও হয়তো আরেকটু গর্ব করতে পারতাম।
অনেককিছু হারিয়ে গেলেও এখনো চেষ্টা করলে হয়তো টিকিয়ে রাখা যাবে কোচদের ভাষা। চাইলে খুঁজে পাওয়া যাবে কোচদের ইতিহাস। কিন্তু ভাষার মাসে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে যে জাতি তার দায়িত্ব শেষ করে তাদের কাছে অন্য ভাষার গুরুত্ব কতটা তা একটি প্রশ্ন মাত্র।