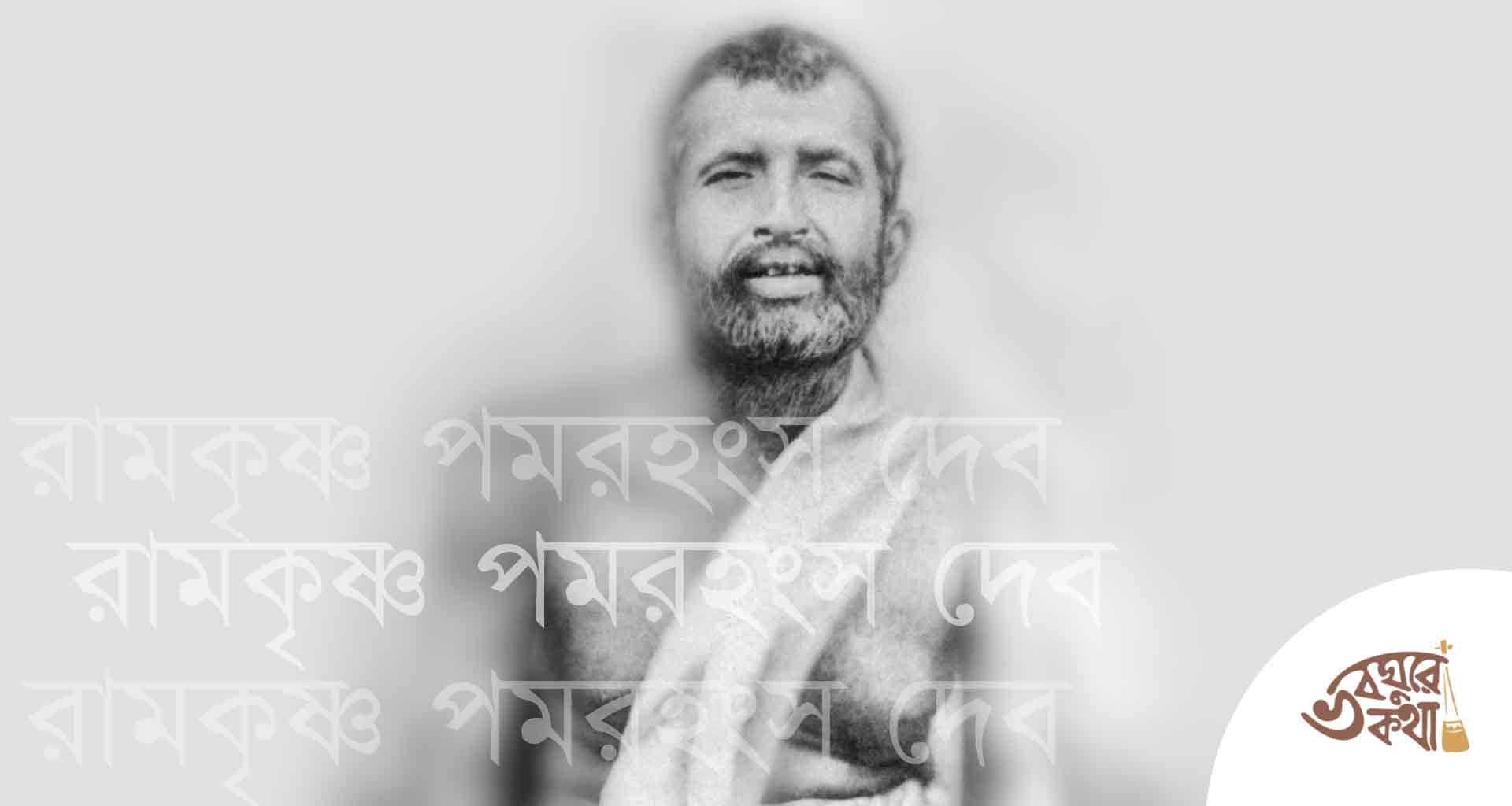মাস্টার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বপ্রণিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে’ ‘শ্রীম’, ‘মাস্টার’, ‘মণি’, ‘মোহিনীমোহন’ বা ‘একজন ভক্ত’ ইত্যাদি ছদ্মনাম বা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন; কারণ তাঁহার অনুপম কীর্তিসৌরভ আপনা হইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে।
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের শ্যামবাজারস্থ শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজন্য তিনি ‘মাস্টার’ মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমনকি, ঠাকুরও তাঁহাকে কখন মাস্টার বলিয়া অভিহিত করিতেন।
‘কথামৃতে’র আদিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এও শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে –
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসত্যই শত সহস্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তির গৃহপার্শ্বে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করাইয়া সর্বোত্তম ফলদানের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চ খণ্ডএ বিভক্ত এই গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সহজ সাবলীল গতি, ভাবের গাম্ভীর্য, স্বল্প কথায় সজীব চিত্রাঙ্কন, সর্বজনীন সহানুভূতি, অসীম উদারতা ও অবাধ অন্তর্দৃষ্টির সুনির্মল দর্পণরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে উচ্চাসন অধিকারপূর্বক লেখককে অমর করিয়াছে।
একটি জীবনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইলেও মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্বীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপূর্ণ মৌখিক উপদেশপ্রভাবে শত সহস্র দুর্বল ধর্মপথচারীর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উজ্জ্বল আলোক তুলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা জাগাইয়াছেন।
তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার গুণে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কয়েকটি বৎসরের চিত্র শ্রোতাদের সম্মুখে সচল হইয়া উঠিত; ঠাকুরের পূত-সঙ্গলাভে ধন্য দিবসগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে ওই চিত্রসমূহ সমুজ্জ্বল হইয়া এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করিত এবং সমাগত ধর্মপিপাসুদিগকে অবলীলাক্রমে সেই সজীব পুরাতন লীলাক্ষেত্রে উপস্থানপূর্বক শান্তি ও বিশ্বাসের শুর্ব পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত।
মাস্টার মহাশয় সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুকুরের স্মৃতিরাজ্যে বাস করিতেন এবং বাহিরের যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সেই রাজ্যেরই কোন ঘটনা চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে উহারই সহিত বিজড়িত অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত। শ্রোতা আসিয়া যে-কোন বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না কেন, অমনি উত্তরছলে তিনি জীবন্ত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের কিয়দংশ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ এই স্বেচ্ছাধৃত ব্রতই উদ্যাপন করিয়াছিলেন।
১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই (১২৬১ বঙ্গাব্দের ৩১শে আষাঢ়) শুক্তবার নাগপঞ্চমী দিবসে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাস লেনের পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা শ্রীমধুসদন গুপ্ত ১৩/২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের গৃহখানি ক্রয়পূর্বক তথায় চলিয়া আসেন। গৃহখানি অদ্যবধি বর্তমান এবং ওই অঞ্চলের ‘ঠাকুরবাড়ি’ বলিয়া পরিচিত। পিতা মধুসূদন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভয়েই সরলতা, মধুর ব্যবহার ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।
তাঁহাদের চারিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। মাতার স্নেহ ও সদ্গুণরাশি মহেন্দ্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল। মাতার সহিত তাঁহার যে বহু অপূর্ব শৈশবস্মৃতি বিজড়িত ছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন চারি বৎসরের বালক মহেন্দ্র মাতার সহিত নৌকাযোগে মাহেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকালে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর দর্শনমানসে চাঁদনীর ঘাটে নামিয়া যখন নব-নির্মিত উদ্যান ও মন্দিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন।
তখন কালী-মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত বালক অকস্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। অমনি শ্রীমন্দির হইতে নির্গত এক সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলে বালক সুস্থ হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকে। উত্তরকালে মাস্টার মহাশয় এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, “হয়তো বা ঠাকুরই হবেন; কারণ তার কিছুদিন (চার বৎসর) আগে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুর তখন মা-কালীর পূজকপদে রয়েছেন।”
আর একবার পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত এক সুবৃহৎ ছাদে অবস্থানপূর্বক অসীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে অনন্তের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। বৃষ্টির সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিঝুম বারিপাতের মধ্যে অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইতেন। কালীঘাটের ছাগবলি তাঁহাকে ব্যথিত করিত। মাতার সহিত উহা দর্শনান্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে উহা বন্ধ করিতে হইবে।
কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসিল, তখন পরিণতবয়স্ক মাস্টার মহাশয়ের চিন্তাধারায় আমূল পরিবত্রন ঘটিয়াছে; সুতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে কৈশোরেই ফেলিয়া চলিয়া যান। সেদিন মহেন্দ্র অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, জননী সস্নেহে বলিতেছেন, “আমি এযাবৎ তোকে লালন-পালন করেছি, পরেও তাই করব; তবে তুই দেখতে পাবি না।” জগদম্বা পরে সত্যসত্যই তাঁহার লালনের ভার লইয়াছিলেন।
মহেন্দ্রনাথের জীবনে একটা এক টানা ধর্মভাব সর্বদাই পরিস্ফুট ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে?” তখন মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা হাঁ! তখন খুব কম বয়েস – নয়-দশ বৎসর বয়স – এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম!” কোন দেবমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গমনাগমনকালে তিনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিতেন। ৺দুর্গাপূজার সময় দীর্ঘকাল ভক্তিভরে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন।
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া সমাজমন্দিরে এবং ‘কমল কুটীর’ প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এ-প্রকার আকর্ষণ-শক্তির কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত এবং দেবতা বলে মনে হত তার কারণ তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না করে প্রচার করছেন।”
যোগাদি উপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রাব্যপদেশে কলিকাতায় সাধুসমাগম হইলে তিনি তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির জন্য আকুল হইতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুসঙ্গ-স্পৃহাই তাঁহাকে এককালে সর্বোত্তম সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আনয়নপূর্বক জীবন সার্থক করিয়াছিল। বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠের সময় তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ইত্যাদি গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন।
পাঠ্যগ্রন্থেও ধর্মভাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে করিয়া রাখিতেন। ‘কুমারসম্ভবে’ যেখানে শিবের ধ্যানবর্ণনাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, গুহাভ্যন্তরে মহাদেব সমাধিমগ্ন, আর গুহাদ্বারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল জীব ও সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করিতে আদেশ দিতেছেন – আর সে অলঙ্ঘ্য নির্দেশে বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহগকুল মূক, পশুবৃন্দ নিশ্চল এবং সমগ্রকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।
অথবা ‘শকুন্তলা’য় যেখানে কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিংবা ‘ভট্টিকাব্যে’ যেখানে রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কাবধার্থে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্বক তত্রত্য বৃক্ষলতাদিকে যজ্ঞধূমে কজ্জলবর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছেন – সেই-সব স্থল তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মতো ওই বই পড়তাম।”
বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের সহিত তিনি এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবার জন্য বাইবেলের বাক্য অনর্গল উদ্ধৃত করিতে থাকিতেন। আইন-অধ্যয়নকালে তিনি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি হইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্মকথা শিখিয়া লইয়াছিলেন; তাই পরে বলিতেন, “ওকালতি কর আর নাই কর, আইন পড়ো; কারণ তাতে ঋষিদের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুন অনেক জানতে পারবে।”
বিদ্যালয়ে বুদ্ধিমত্তার জন্য মহেনদ্রনাথের সুনাম ছিল। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকারপূর্বক হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পরীক্ষায় তাঁহার স্থান ছিল পঞ্চম। অতঃপর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাদ্বে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্বক প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজী, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগসহকারে আয়ত্ত করেন। ইংরেজীর অধ্যাপক টনি সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন।
কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি শ্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা এবং কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নীসম্পর্কীয়া শ্রীমতি নিকুঞ্জদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১৮৭৩)। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশান্তে তাঁহার অধ্যয়ন আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু সংসারের আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাঁহাকে ওই সঙ্কল্প ত্যাগপূর্বক সওদাগরি অফিসে চাকরি লইতে হইল।
পরে অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হইয়া তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের পদ শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। অনেক সময় একই কালে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি পালকিতে যাতায়াত করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার গাম্ভীর্য, ধর্মভাব ও সহজ অধ্যাপনাপ্রণালীতে আকৃষ্ট হওয়ায় পাঠকালে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁহাকে বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বস্তুতঃ কার্যে তিনি সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া সমাজমন্দিরে এবং ‘কমল কুটীর’ প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এ-প্রকার আকর্ষণ-শক্তির কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত এবং দেবতা বলে মনে হত তার কারণ তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না করে প্রচার করছেন।”
কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না – তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের দেবী মৃন্ময়ী নহেন, চিন্ময়ী! মাস্টার তখনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাই যদি সত্য হয় তবে যাঁহারা প্রতিমায় উপাসনা করেন, তঁহাদিগের তো বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, বস্তুতঃ মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নহে, প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, “কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেক্চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া!
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও নিজের আত্মীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের স্বল্পকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হওয়ায় উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মহেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিবস বরাহনগরে ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কবিরাজের গৃহে আশ্রয় লইলেন।
এই বাটীতে অবস্থানকালে তিনি এক সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে রত আছেন। সুন্দর দেবালয়ের পবিত্র আবেষ্টন। সম্মুখে ঠাকুর যেন শুকদেবের ন্যায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া ভগবৎগুণকীর্তন করিতেছেন।
ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কুতূহলী কবিসুলভ মন দেবোদ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য তাঁহাকে বাহিরে লইয়া চলিল। উদ্যানপর্যবেক্ষণান্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। অচিরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঠাকুর অন্যমনস্ক হইতেছেন দেখিয়া মাস্টার ভাবিলেন, “ইনি ঈশ্বরচিন্তা করিবেন”, অতএব বিদায় লইলেন। গমনকালে ঠাকুর বলিয়া দিলেন, “আবার এসো।”
দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেলা আটটায়। ঠাকুর পুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসান্তে অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কি না। মাস্টার কহিলেন, “আজ্ঞে হাঁ!” অমনি ঠাকুর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “ওরে রামলাল, যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে!” তারপর তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, মাস্টারের একটি ছেলেও হইয়াছে।
উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া-দর্শনে মাস্টার মহাশয়ের প্রতীতি হইল যে, এযাবৎ যদিও তিনি ধর্মর্চচা ও উপাসনাদি করিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধার্মিকের দৃষ্টিতে তিনি জাগতিক স্তরের অধিক ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। এইরূপে তাঁহার অভিমান প্রতিপদে চূর্ণীকৃত হইতে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ উৎসাহশূন্য না করিয়া যেন সান্ত্বনাচ্ছলেই বলিলেন, “দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল – আমি কপাল চোখ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে পারি।”
ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও মাস্টার মহাশয়কে শীঘ্রই আরও কয়েকটি আঘাতে সম্পূর্ণ অবনত হইতে হইল। ক্যান্ট, হেগেল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত সুপরিচিত মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, মানবজীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এবং যাহার বিদ্যালাভ হইয়াছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু আজ সেরূপ শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান।
অমনি আবার প্রশ্ন হইল, তিনি সাকারে বিশ্বাসী কিংবা নিরাকারে? মাস্টার বলিলেন, তাঁহার নিরাকার ভাল লাগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশ্বাস থাকা উত্তম বটে, তবে সাকারও সত্য। এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসদ্বয় কিরূপে সত্য হইতে পারে, তাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চূর্ণ হইল।
কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না – তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের দেবী মৃন্ময়ী নহেন, চিন্ময়ী! মাস্টার তখনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাই যদি সত্য হয় তবে যাঁহারা প্রতিমায় উপাসনা করেন, তঁহাদিগের তো বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, বস্তুতঃ মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নহে, প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, “কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেক্চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া!
যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তোমার মাথাব্যাথা কেন? তোমার নিজের যাতে জ্ঞানভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।” মাস্টারের অভিমানের সৌধ একেবারে ভূমিসাৎ হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম অনুভূতির বস্তু – বুদ্ধি ততদূর অগ্রসর হইতে পারে না; বুদ্ধিরূপ দুর্বল যন্ত্র-সাহায্যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না।
এবং তাদৃশ তত্ত্বলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী সাধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্যক – তদ্ব্যতীত অতি মার্জিত বুদ্ধিও আমাদিগকে ভগবৎসকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ঢালিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।
.. ভক্তি থাকলেও স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। ….. সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।” আর উপদেশ দিয়েছিলেন, “ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ – ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।”
আরও কিছুদিন বরাহনগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশয় উপর্যুপরি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গনমাগমন করিয়া অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরের ও মাস্টারের প্রতি কার্যে ও কথায় ওই অন্তরঙ্গ সহজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপে ওই বৎসর একদিন মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদিগকে বলিলেন,
“ওইরে আবার এসেছ!” বলিয়াই অহিফেনের দ্বারা বশীকৃত একটি ময়ূরের গল্প বলিলেন – ওই ময়ূরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আফিম দেওয়া হইত এবং ময়ূরেরও এমনি মৌতাত ধরিয়াছিল যে, সে প্রত্যহ ঠিক সময়ে একই স্থানে উপস্থিত হইত। মাস্টার মহাশয়ের সত্যই তখন মৌতাত ধরিয়াছে। তিনি গৃহে বসিয়া দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা করেন; দীর্ঘ বিরহ অসহ্য বোধ হইলে ছুটিয়া শ্রীগুরুপদে উপস্তিত হন।
একবার বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজে ঘর্মাক্ত-কলেবরে মহেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগত দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “এর মধ্যে (নিজের দেহ দেখাইয়া) কি একটা আছে যার টানে ইংলিশম্যানরা (ইংরেজী-শিক্ষিতেরা) পর্যন্ত ছুটে আসে।” এই টানের কারণ নির্দেশ করিয়া ঠাকুর একদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলিকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হল না, তোমার হল কেন? এর কারণ জন্মান্তরে সংস্কার।”
আর একবার বলিয়াছিলেন, “দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে – এ-সব তো আমি জানি!” অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, “সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম – তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম।” আরও পরিষ্কার করিয়া একসময়ে কহিলেন, “তোমায় চিনেছি – তোমার ‘চৈতন্য-ভাগবত’ পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা – যেমন পিতা আর পুত্র।”
এরূপ সংস্কারবান উচ্চাধিকারীকে ঠাকুর উপদেশ ও সাধনা-সহায়ে ক্রমে অনুভূতির ঊর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর স্তরে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত সুপরিচিত থাকায় তাঁহাকে সদ্গৃহস্থ হইবারই উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার মনে কখনও বৈরাগ্য আসিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবৃত্ত করাইতেন। একদিন তাই জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, “সব ত্যাগ করিয়ো না, মা।
…. সংসারে যদি রাখ, তো এক একবার দেখা দিস – না হলে কেমন করে থাকবে? এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে, মা? – তারপর, শেষে যা হয় করো।” অপরাপর দিবসে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন, “ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক। তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।”
“আর বাপের সঙ্গে প্রীত করো। এখন উড়তে শিখে বাপকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? …. মা আর জননী – যিনি জগৎরূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই মা।” “যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী; ….. অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।” আবার একটু পরেই এইরূপ কঠোর আদেশ শ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টারের নিকটে গিয়া তত্ত্বকথা শুনাইলেন, “কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে।
.. ভক্তি থাকলেও স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। .. সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।” আর উপদেশ দিয়েছিলেন, “ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ – ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।”
অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন – যেমন আইন-অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে;” আর তিনিই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জানাইলেন, “আমার মনে হয় যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক।” ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করিয়া মাস্টার যখন বলিলেন যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি সে ফাঁকটি কি?” মাস্টার বলিলেন, “সে ফোকর আপনি।”
“ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। ….. তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। ….. ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।”
ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানতঃ শুদ্ধাভক্তিরই উপদেশ দিতেন। একদিন বলিলেন, “দেখ, তুমি যা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে – আর না। বল, আর করবে না।” মাস্টার যুক্তকরে বলিলেন, “আজ্ঞে, না।” মাস্টার স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। নৃত্যকালে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “এই শালা, নাচ!” আর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন সর্বদা ভগবদালাপ করিতে।
একদিন মাস্টার ও নরেন্দ্র বিদ্যলয়ের ছাত্রদের নৈতিক অবনতির কথা আলোচনা করিতেছেন জানিয়া মাস্টারকে বলিলেন, “এ-সব কথাবার্তা ভাল নয় – ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।” এইরূপে সাধুসঙ্গ, নির্জন-বাস এবং ভগবদালাপনের সঙ্গে ব্যকুলতার প্রয়োজনও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।” এইসব স্থলে ব্যাকুলতার উল্লেখ দেখিয়া এবং পূর্বে বিচার-বিষয়ক নিষেধবাক্য শুনিয়া পাঠক যেন মনে করিবেন না যে, ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে ভাবুকতায় ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন।
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে যে বৃথা তর্কপ্রবণতা আসে এবং ভগবৎসম্বন্ধহীন বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহে জন্মে, মাস্টার মহাশয়কে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি, “সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার – কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয় …. এই পর্যন্ত; ভগবানলাভ হয় না! তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, এর নাম বিচার। বুঝেছ?”
মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে যান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং সমস্ত ব্যাপার ও পরিবেশটি স্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে পূর্বাভ্যাসানুসারে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া রাখেন। এই প্রকারেই যথাকালে ‘কথামৃতে’র সৃষ্টি হয়।
মাস্টার মহাশয় প্রথমতঃ নিরাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে অদনুরূপ উপদেশই দিতেন। একবার মতি শীলের ঝিলে ক্রীড়ারত মৎস্যগুলিকে দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মে ওইরূপে মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। মাস্টার সেই পথেই চলিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে একদিন তিনি স্বীকার করিলেন, “আমি দেখছি, প্রথমে নিরাকারে মন স্থির করা সহজ নয়।”
ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, “দেখলে তো? তাহলে সাকার-ধ্যানই কর না কেন?” মাস্টার উহা অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্বক তাঁহারই নির্দেশানুসারে ধ্যানভজনাদি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও অধিকাধিক হইতে লাগিল; অবসরমত দুই-চারিদিন তিনি সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় সমগ্র ডিসেম্বর মাসটি তিনি শ্রীগুরুসকাশে যাপন করেন।
এদিকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মাস্টার মহাশয়ের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “এইরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই;” তিনিই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বীকার করিলেন, “আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন।
অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন – যেমন আইন-অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে;” আর তিনিই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জানাইলেন, “আমার মনে হয় যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক।” ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করিয়া মাস্টার যখন বলিলেন যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি সে ফাঁকটি কি?” মাস্টার বলিলেন, “সে ফোকর আপনি।”
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহীন, তখন বিরল দুই-চারিজন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সৎপরামর্শ দিয়া বরাহনগরের মঠ-সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। ছুটির দিনে প্রায়ই ওই মঠে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল কথা স্মরণপূর্বক স্বামী বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,
অমনি ঠাকুর তাঁহার গা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, “তুমি যে ওইটে বুঝে ফেলেছ – বেশ হয়েছে!”
শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে অসুস্থ, তখন মাস্টার কামারপুকুরদর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ধমান হইতে অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। সেই পথে সে সময়ে দস্যুর উপদ্রব ছিল; তাই পথিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। তখন মাস্টারের চক্ষে নবানুরাগের অঞ্জন – দূর হইতে কামারপুকুর দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, কামারপুকুরের পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই অভিবাদন জানাইলেন; আর সর্বত্রই ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত জানিয়া পুলকিতচিত্তে সবই দর্শন-স্পর্শন করিতে লাগিলেন।
রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর এই সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, তার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির অধিক্য আপনা থেকে এত কষ্ট করে ওইসব জায়গায় গিয়েছিল – কারণ আমি সে সব জায়গায় যাতায়াত করতাম। এর ভক্তি বিভীষণের মতো। বিভীষণ মানুষ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পূজো-আরতি করত, আর বলত, এই আমার প্রভু রামচন্দ্রের একটি মূর্তি।”
আর কামারপুকুর হইতে প্রত্যাগত মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “কি করে গেলে ও-ডাকাতের দেশে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব।” সশরীরে একসঙ্গে যাওয়া অবশ্য হয় নাই; কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তিনি তাঁহাকে আরও আট-নয় বার কামারপুকুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কামারপুকুরের প্রতি মাস্টার মহাশয় একসমেয় এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করেন।
মা কিন্তু সহাস্যে বলেন, “বাবা, ও-জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো – ওখানে থাকতে পারবে না।” অবশেষে মায়ের আদেশই প্রতিপালিত হইল।
বাল্যের ন্যায় যৌবনেও মাস্টার মহাশয় প্রকৃতিক সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও অসীমতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হস্তের আভাস পাইতেন। ঠাকুরের লীলাকালে তিনি একবার কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখর দর্শনপূর্বক আনন্দে আপ্লুত ও ভক্তিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবতর্তনের পর ঠাকুর তাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?”
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত মাস্টারের তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। স্বভাবতঃ লাজুক মাস্টারের মুখে কিন্তু তখন কথা ফুটিত না; তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না।” আর একদিন তিনি গান গাহিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ও স্কুলে দাঁত বার করবে; আর এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা।” কখনও বা বলিতেন, “এর সখীভাব।”
যাহা হউক, এই নম্রপ্রকৃতির মানুষটির সহিত পুরুষসিংহ নরেন্দ্রের প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে কোনও বাধা হয় নাই। পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য যোগাড় করিয়া দেন; একবার নরেন্দ্রের বাড়ির তিন মাসের খরচ চালাইবার জন্য একশত টাকা দেন; এতদ্ব্যতীত গোপনে নরেন্দ্র-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, নরেন্দ্রকে যেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনি উহা প্রত্যবর্তন করিবেন।
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহীন, তখন বিরল দুই-চারিজন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সৎপরামর্শ দিয়া বরাহনগরের মঠ-সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। ছুটির দিনে প্রায়ই ওই মঠে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল কথা স্মরণপূর্বক স্বামী বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,
“রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে – হাবাতে (গরীব ছোঁড়াগুলি) মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেশ (সুরেন্দ্র মিত্র), মাস্টার ও চুনীবাবু – এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।”
তাই তিনি যখন নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, তখন অনুভব হইত যেন কোন শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশান্তললাট, সৌম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক ঋষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের গার্গীর দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ খ্রী:) ওই অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি আবেগে এতই অভিভুত হইয়া পড়েন যে, সামলাতে না পারিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; অনেক্ষণ বাতাস করার পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।
শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে জাগতিক দৃষ্টিতে বিছিন্ন মাস্টার মহাশয় তীর্থদর্শন সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন এবং শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজীর দর্শনলাভে ধন্য হন। তাঁহার সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এক সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটীরে তপস্যায় রত হন, কিন্তু আর্দ্র গৃহে কঠোর জীবনযাপনের ফলে অসুস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ায় স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে গাড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যান।
বরাহনগরের মঠে বাসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরেও তিনি মধ্যেমধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন। আর এক অদ্ভ্যুত খেয়াল ছিল তাঁহার, স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি গভীর রাত্রে গাত্রোত্থানপূর্বক শয্যা লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বারান্দায় উপস্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহীনদের মধ্যে শয়নপূর্বক আপনাতেও সহায়সম্বলহীন গৃহশূন্য ব্যক্তির অবস্থা-আরোপের চেষ্টা করিতেন।
পরে কেহ যদি ওই গুপ্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিত, “এত কঠোরতা করতেন কেন?” তিনি উত্তর দিতেন, “গৃহ ও পরিবারের ভাব মনে থেকে যেতে চায় না, আঠার মতো লেগে থাকে।”
পর্ব উপলক্ষে তিনি গঙ্গাতীরে সমবেত সাধুদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে যাইয়া দেখিতেন, মুক্তাকাশতলে কেমন তাঁহার প্রজ্বলিত অগ্নিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বা জপরতা রহিয়াছেন। কখনও হাওড়া স্টেশনে যাইয়া জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা মহাপ্রসাদ চাহিয়া খাইতেন – উদ্দেশ্য, এইভাবে ওই মহাতীর্থে গমনের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ফললাভ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চির সামীপ্যবোধের জন্য তিনি দিবাভাগেও অবসরকালে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলিয়া শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পাঠ ও ধ্যান করিতেন।
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরিনীর সহিত কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দ্দিবস যাপনানন্তে প্রায় একবৎসর তীর্থভ্রমণাদি করেন। এই অবকাশে তিনি মাসাধিককাল কনখল সেবাশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে একটি কুটিয়ায় থাকিয়া তপস্যা করেন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন; তাঁহার সহিত ভ্রমণ ও আলোচনাদি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার পরে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া ঝুলন দর্শন করেন এবং রাসধারীদের অভিনীত ‘কৃষ্ণ-সুদামা’র পালা দেখিয়া আহ্লাদিত হন।
প্রকাশ্যে এই-সকল সাধনা ছাড়াও অনাড়ম্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হইত। ঋষিদের ভাব আপনাতে আরোপ করিবার জন্য তিনি কখন হবিষ্যান্ন-ভোজন বা পর্ণকুটিরে বাস করিতেন; কখন বা বৃক্ষমূলে একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, আর বিশাল আকাশ, গগনচুম্বী পর্বত, অপার সমুদ্র, সমুজ্জ্বল তারকামণ্ডলী, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, সুন্দর নিবিড় বনানী, সুকোমল সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরীয় চিন্তা সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ঋষিদের তপোভূমিতে লইয়া যাইত।
সুযোগ পাইলেই তাঁহার অন্তনির্হিত সাধনাভিলাষ উদ্দীপিত হইত। এইরূপে ১৯২৩ অব্দে মিহিজামে পাকা বাটী থাকা সত্ত্বেও তিনি নয় মাস পর্ণকুটিরে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুরীতে চারি মাস নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন ছিল উচ্চসুরে বাঁধা; প্রভাতসূর্য দেখিলেই দিব্যভাব-গ্রহণে সদা উন্মুখ মাস্টার মহাশয়ের মুখে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হইত। ফলতঃ সর্বদা প্রাচীনের চিন্তাধারায় আপ্লুত মাস্টার মহাশয়ের দেহমনে প্রাচীনের একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল।
তাই তিনি যখন নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, তখন অনুভব হইত যেন কোন শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশান্তললাট, সৌম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক ঋষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের গার্গীর দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ খ্রী:) ওই অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি আবেগে এতই অভিভুত হইয়া পড়েন যে, সামলাতে না পারিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; অনেক্ষণ বাতাস করার পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।
সে মধুর আলাপনে লুব্ধ বহু ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যাত্মতীর্থে অবগাহন করিতে যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্গ্রন্থপাঠ চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল অংশ সরল কিংবা সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অনর্গল অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, উপনিষদাদি হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক, কিংবা যীশু, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনের অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসাইয়া রাখিয়াছেন।
গৃহে থাকিলেও তাঁহার সাধুচিত অশেষ সদ্গুণরাশি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রাতে স্নানান্তে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন। সর্বদা এই চিন্তা মনে জাগাইয়া রাখিতেন যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বস্তুর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, আর বলিতেন, “মৃত্যুচিন্তা থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না বা কোনও জিনিসে আসক্তি থাকে না।” সংসারের প্রয়োজনেও তিনি কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতে পারিতেন না।
অন্যায় দেখিলে বলিতেন, “যার যেরকম স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে – মানুষের আর দোষ কি?” সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী – নিকটে ভৃত্য থাকিলেও তাহার সেবাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেন। এমনকি, আটাত্তর বৎসর বয়সে স্নায়ুশূলে হস্ত নিদারুণ ব্যথিত হইলেও যন্ত্রণা-উপশমের জন্য স্বহস্তে পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক দিতেন। আবার এত সদ্গুণের আধার হইয়াও প্রশংসা-শ্রবণে উত্যক্তস্বরে বলিতেন,
“Mutual admiration (পারস্পরিক প্রশংসা) রেখে দাও।” নিরাভিমান মাস্টার মহাশয় ‘আমি, আমার’ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বহুবচন পরয়োগ করিতেন বা গৌণভাবে কথা কহিতেন। তাঁহার বাড়ির প্রচলিত নাম ছিল ‘ঠাকুর বাড়ি’। তিনি কখন কখন ভবানীপুরে গদাধর-আশ্রমে থাকিতেন। একবার ওইরূপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্যোপলক্ষে উত্তর কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্টিত বিদ্যালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া যাইতেন,
“আমি এখানে খাব না – এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি।” ভক্ত আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং।
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাদির পর তিনি ঝামাপুকুরে মর্টন ইন্স্টিটিউট ক্রয় করেন। বিদ্যালয় পরে ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটীর চার তলায় ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন এবং তুলসী ও পুষ্পবৃক্ষে সজ্জিত গৃহছাদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মালাপ করিতেন। ওই কক্ষই ছিল তাঁহার বাসস্থান বা আশ্রম; দিবসে একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বগৃহে যাইয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিতেন।
ক্রমে এইটুকু সংসার-সম্পর্কও তিরোহিত হইয়া তাঁহাকে ভগবৎপ্রসঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রদান করিল। ‘কথামৃত’ প্রকাশের পর দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্ত পিপাসা মিটাইতে তাঁহার নিকট আসিত এবং মাস্টার মহাশয়ও তাঁহাদিগকে স্বীয় ভাণ্ড উজাড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।
শেষজীবনে যাঁহারা মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার বাসস্থান তখন প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমিতে পরিণত হইয়াছিল – সংসারের প্রবল তরঙ্গদ্বেলিত স্রোত নিম্নে প্রবাহিত, আর রাজপথের কোলাহলের ঊর্ধ্বে হিমালয়ের নীরবতা বিরাজিত! যখন যিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জ্ঞান-ভক্তির আলোচনাতেই মগ্ন! ভক্ত ও সাধু-সঙ্গে তাঁহার অসীম আনন্দ, অবিরাম ভগবদালাপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাধিক মিলনের আগ্রহ না দেখিয়া থাকিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।
সে মধুর আলাপনে লুব্ধ বহু ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যাত্মতীর্থে অবগাহন করিতে যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্গ্রন্থপাঠ চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল অংশ সরল কিংবা সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অনর্গল অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, উপনিষদাদি হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক, কিংবা যীশু, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনের অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসাইয়া রাখিয়াছেন।
মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাগের মহিমা এইরূপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, “সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বুঝা যায়।” আর একজনকে বলিয়াছিলেন, “হয় সাধুসঙ্গ, না হয় নিঃসঙ্গ! বিষয়ীদের সঙ্গ করলেই পতন।” আবার বলিতেন, “যখন সাধুসঙ্গ পাওয়া যাবে না, তখন সাধুদের ফটো বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে।”
কেহ অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি কৌশলে আলোচনার ধারাকে ভগবন্মুখী করিয়া দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টার মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন, “যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে। ভগবানের বানী যারা প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা না হলে তাঁর কথা বলবে কারা?
সেইজন্য মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন।” শ্রীশ্রীজগদম্বার মহিমাপ্রচারের জন্য ঠাকুর যাঁহাদিগকে ‘চারপাশ-প্রাপ্ত’ বলিয়া মনে করিতেন, মাস্টার মহাশয় ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম।
শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের প্রতি মাস্টার মহাশয়ের প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও কাহারও ছবি স্বগৃহে রাখিয়া তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ অসুখের সময় তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পরও নিজের বিছানায় পড়িয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) প্রভৃতি যুবকগণ যদিও রিপণ কলেজে তাঁহারই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাঁহার ধর্মভাবের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা রামবাবুর আকর্ষণে কাঁকুড়গাছিতে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল; অথচ রামবাবুর তদানীন্তন ধারণা ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিতেন, “বিলে (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তো ঠাকুরকে মানতই না, তর্ক করত,
“ঠাকুরকেই যদি ভগবান বলে বিশ্বাস হল, তবে তাঁর কথাই তো শাস্ত্র; অপর শাস্ত্রের দরকার কি? ঠাকুরকে বকলমা দিলেই হল; আর কোন সাধন-ভজনের দরকার নেই। সংসারের মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি কৃপা করবেন” ইত্যাদি। অতএব কাঁকুড়গাছিতে তাঁহারা বরাহনগর মঠ কিংবা মঠবাসী সাধুদের কোন সংবাদই পান নাই।
এদিকে তাঁহাদের উৎসুক নয়ন শীঘ্রই আবিষ্কার করিল যে, তাঁহাদের গম্ভীরপ্রকৃতি ও বেশভূষায় পারিপাট্যহীন মাস্টার মহাশয় কলেজের অবসরকালে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকখানি (অর্থাৎ ‘কথামৃত’) নিবিষ্টমনে পড়েন। তাঁহার অন্যন্য চাল-চলনও একটু অসাধারণ। অতএব তাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহেও গেলেন।
মাস্টার মহাশয় মাদুর পাতিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং নিজেও পার্শ্বে বসিলেন – আধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সাধারণতঃ যে কায়দাদুরস্ত ব্যবহার দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিল না। এইরূপে যুবকদিগের হৃদয় জয় করিয়া লইয়া মাস্টার বলিলেন, “দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী; তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রকৃত বাণি পেতে হলে, তাঁর যে-সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়; গৃহস্থেরা হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক বলতে পারে না।”
এই উপদেশের ফলে এই যুবকগণ বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং যথাকালে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্বল করেন।
মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাগের মহিমা এইরূপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, “সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বুঝা যায়।” আর একজনকে বলিয়াছিলেন, “হয় সাধুসঙ্গ, না হয় নিঃসঙ্গ! বিষয়ীদের সঙ্গ করলেই পতন।” আবার বলিতেন, “যখন সাধুসঙ্গ পাওয়া যাবে না, তখন সাধুদের ফটো বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে।”
“গুরুজন যা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ।” আর ছিল তাঁহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না – সে সাধু বয়সে যতই ছোট হউক না কেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওটা করবেন না। ‘তৃণাদপী সুনীচেন’ – ও থাক। ঠাকুর বলতেন, ‘এই দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্য আসনে বসাতে হয়।’ যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা শুনতে হয়।”
এইসব উপদেশ দিয়া তিনি আরো বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মর্মকথা ছিল ত্যাগ; এমনকি, গৃহস্থদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যেও ত্যাগের বীজ লুক্কায়িত থাকিত এবং বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে এই জন্মেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইত; অপর স্থলে ভাবী জন্মে ওইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। জনৈক ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,
“দেখ না, তিনি চন্দ্রসূর্যকে আলো ও উত্তাপ দেবার জন্য রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন – আমরা দেখে অবাক্। লোকের চৈতন্য হবার জন্য তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধুরাই তাঁকে বেশি ধরতে পারেন। তাঁরা সোজা পথে উঠেছেন, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন।” ভক্ত আপত্তি জানাইলেন, “এই যে সব সাধুরা আসেন, এঁরা কি সকলেই সর্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আসছেন?”
মাস্টার মহাশয় ঈষন্মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, “এঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন! চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। সংসারীরা কলঙ্কসাগরে মগ্ন হয়েও আবার কলঙ্ক অর্জন করছে। …. সাধুরা যদি অন্যায়ও করে তবু আবার ঝেড়ে ফেলতে পারে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ।” সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সদালাপ করিতেন আর বলিতেন,
“সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন! এঁর জন্য আমার স্নানাহার বন্ধ রাখতে হবে। তা যদি না করতে পারি তবে এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য আর কিছু হতে পারে না।” সাধুদিগকে তিনি শুধুমুখে ফিরিতে দিতেন না – কিছু না কিছু অবশ্যই খাওয়াইতেন, আর বলিতেন, “আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি – আমি পূজা করছি ও তাই দেখছি।”
বস্তুতঃ তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাঁহার মুখে সাধুর উচ্চ আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সাধুরাও নিজ আদর্শ সম্বন্ধে সমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে অধিকতর যত্নবান হইতেন।
যে-কোন ঘটনা বা বিষয় অবলম্বনে ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, সেই সকলের সংস্পর্শে আসিবার জন্য তিনি নিজে যেমন ব্যাকুল হইতেন, তেমনি পরিচিত সকলকেও তৎতৎ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। উৎসবাদিতে যাইয়া যখন তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভব হইত না, তখন অনুরক্ত ভক্তদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাঁহাদের মুখে সবিশেষ বর্ণনা শুনিতেন। একটি ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,
“দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাবে! কালকে দশহরা – সেখানে পুজো দেখবে। হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, ‘কি করে সর্বদা আপনাকে স্মরণ থাকে?’ রামচন্দ্র বললেন, ‘উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।’ তাই পর্ব-উৎসবে যোগ দিতে হয়।” প্রসাদে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল – উহা ধারণ করিবার পূর্বে ভক্তিসহকারে হস্তে গ্রহণান্তে মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। প্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন,
“গুরুজন যা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ।” আর ছিল তাঁহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না – সে সাধু বয়সে যতই ছোট হউক না কেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওটা করবেন না। ‘তৃণাদপী সুনীচেন’ – ও থাক। ঠাকুর বলতেন, ‘এই দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্য আসনে বসাতে হয়।’ যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা শুনতে হয়।”
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং ইহারই ফলে বহুবার তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যভাবেও অর্থাদির দ্বারা তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত ভক্তদের সহায্যার্থে এবং তপোরত সাধুদের অভাব মিটাইবার জন্যও তিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয় করিতেন। ওইসমস্ত ব্যয়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাঁহার ন্যায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নহে।
স্বয়ং ভগবৎকৃপালাভে ধন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার মহাশয় অপরের সেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের সেবক মনে করিতেন। গুরুর আসন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংবা দীক্ষা কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া যাঁহারা সুদীর্ঘকাল তথায় যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া কিংবা তাঁহাদিগকে নিজস্ব কিছু বলিবার প্রয়াস না করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন।
শাসন তিনি করিতেন না – মুখে ছিল তাঁহার দৈব জ্যোতি, আর জিহ্বায় ছিল অবিমিশ্র আশীর্বাদ। তিনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা না থাকিলে তাঁহার জীবন দুর্বিষহ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া বৃথা স্নেহ প্রকাশপূর্বক তিনি শক্তিক্ষয় বা অনুরাগীকে বিব্রত করিতেন না। সর্বাবস্থাতেই তিনি শান্ত থাকিতেন; সুখ-দুঃখ তাঁহাকে অকস্মাৎ অভিভূত করিতে পারিত না।
জীবন ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য। অবস্থা মন্দ না হইলেও তিনি আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ অতি সাধারণভাবে চলিতেন। তাঁহার মতে ঠাকুরের উপদেশই এই ছিল যে, অনাড়াম্বর জীবনযাপন করিতে হইবে। জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন ও লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্রপরিধানের ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভগদ্ভক্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া আগন্তুকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিত।
ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “মনে ত্যাগ হলেই হল; অন্তঃসন্ন্যাসই সন্ন্যাস।” মাস্টার মহাশয় সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।
‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-প্রণয়নই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ওই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতুম, তখনই বিশেষ ভাবে লিখে রাখতুম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার তিথি নক্ষত্র তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন, “সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি ইচ্ছামত তাঁর কাছে যেতে পারতুম না।
তাই দক্ষিণেশ্বরে যা পেয়েছি তার উপর সংসারের চাপ পড়ে পাছে সব গুলিয়ে খায়, এই ভয়ে আমি তাঁর কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনর্বার যাবার আগে পর্যন্ত ওইসব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম। এভাবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তাঁর উপদেশ আরো ভাল করে জীবনে পরিণত করতে পারি।” এইসকল দিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে লিখিত
‘Gospel of Sri Ramakrishna’ (শ্রীরামকৃষ্ণের-উপদেশ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলেই অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আরও উপদেশ-প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃহত্তর পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এদিকে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে মাস্টার মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় ‘কথামৃত’-রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ অব্দে শ্বামী ত্রিগুণাতীততনন্দ কর্তৃক উহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়।
পরে ক্রমে ১৯০৪ অব্দে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ অব্দে তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অব্দে চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত হিল। ১৯৩২ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়।১ তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন।
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং ইহারই ফলে বহুবার তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যভাবেও অর্থাদির দ্বারা তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত ভক্তদের সহায্যার্থে এবং তপোরত সাধুদের অভাব মিটাইবার জন্যও তিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয় করিতেন। ওইসমস্ত ব্যয়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাঁহার ন্যায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নহে।
শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বৎসর সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীগুরুমহিমা ও বাণী প্রচার করিয়া তিনি ৺ফলহারিণী কালিকা-পূজার পরদিবস ১৯৩২ খ্রী: ৪ঠা জুন (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২০শে জৈষ্ঠ) সকাল সাড়ে ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হন।
পূর্বরাত্রি নয়টার ‘কথামৃত’ পঞ্চম ভাগের প্রুফ দেখিতে দেখিতেই হাতের স্নায়ুশূলের অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং প্রাতঃকালে “মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও” বলিতে বলিতে তিনি চিরনিদ্রায় চক্ষু নিমীলিত করেন। শ্রীগুরুর বাণী-প্রচারে উৎসৃষ্টপ্রাণ মাস্টার মহাশয় শেষমুহূত্র পর্যন্ত ওই কার্যেরই রত থাকিয়া স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিলেন।
স্বামী গম্ভীরানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন,
বেলুড় মঠ, হাওড়া
…………………………………………………
১ ‘শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস’ (সমসাময়িক দৃষ্টিতে), ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।