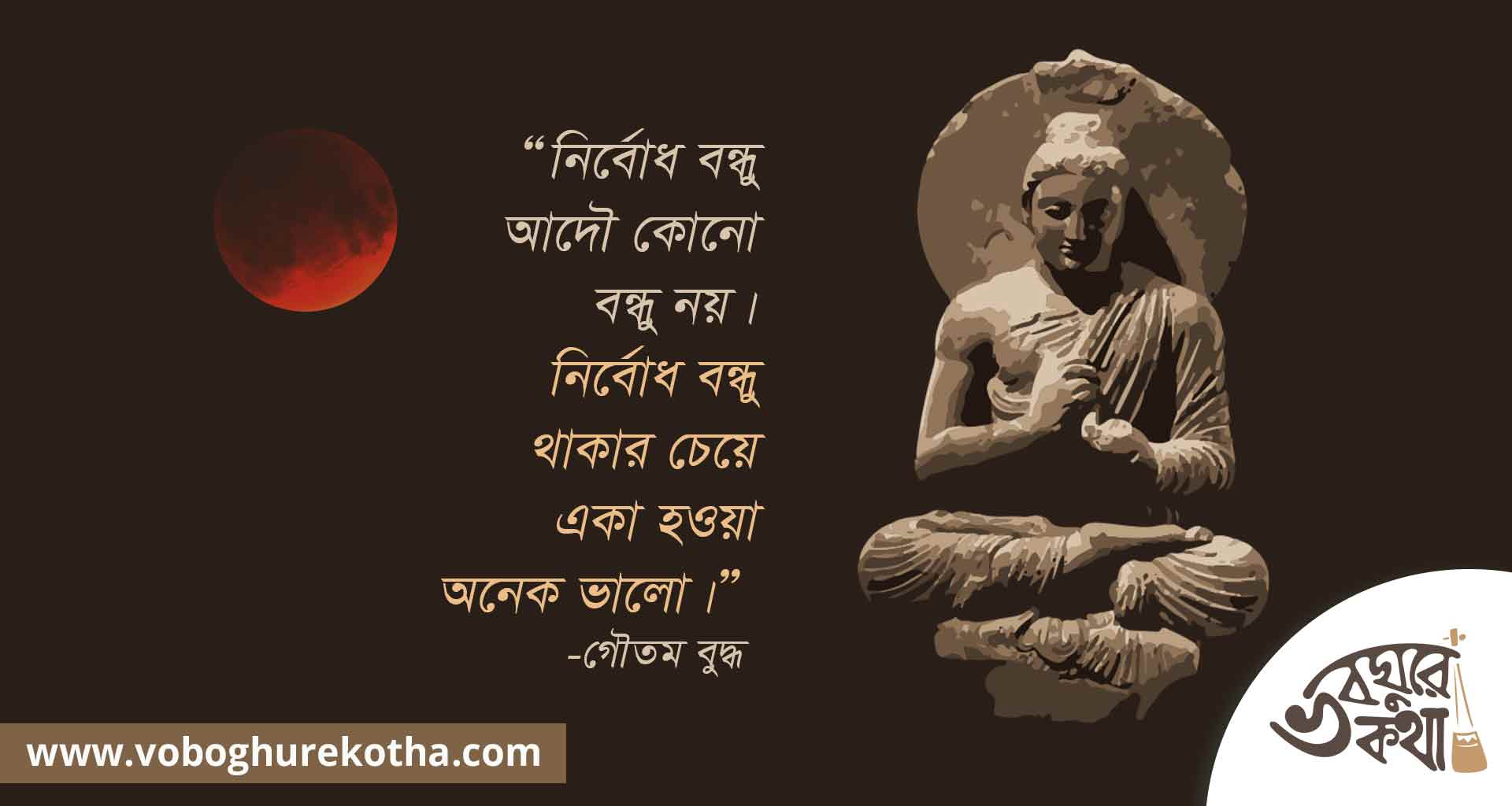-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন।
দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যামকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।
এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, ‘সে কথা যথার্থ- মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি- যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।’
বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখ দু:খের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল।
শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল- মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটো বড়র ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।
সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল ; প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।
[১৩১০ বঙ্গাব্দ]
সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দু:সাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয় স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি।
কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি।
বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান- বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে- বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না।
তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভুত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য-বশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন।
মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বত:প্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।
বুদ্ধদেব বলিয়াছেন-
মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে
এবম্পি সব্বভূতেসু ,মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।।
তিটঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিটঠয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।।
মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূণ্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে।
কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে- ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে। এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে; অমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্যে হইতে সত্য হইয়া উদ্ভুত হইয়াছে।
ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোন স্থানে সত্র হইয়া উঠিয়াছিল।
এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না; এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।
[১৩১১ বঙ্গাব্দ]
বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দু:খ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে।
সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দু:খ, সেইখানেই তার পাপ। এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, ‘তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।’
যে সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন ক’রে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।
সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করেত বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।
[৯ চৈত্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ]
বুদ্ধদেব যে দু:খনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড় আকর্ষণ কী? সে এই যে অত্যন্ত দু:খ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়।
এই দু;খ-স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড় করে জানে। খুব বড় রকম ক’রে ত্যাগ, কুব বড় রকম ক’রে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড় করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।
[১৪ চৈত্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ]
বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্ব চরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকার ত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা।
এমনি করে প্রেম যখন অহং’এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি।
এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুতেই ত্যাগ করে না ; সমস্তকেই সত্যময় ক’রে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।
[৭ বৈশাখ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ]
বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায় না, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিস্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়;
কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।
[৭ পৌষ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ]
বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না- যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দু:খ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনা-লোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়- কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন?
মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ- আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে- বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়- এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে।
আমার ‘পূর্ণিমা’ বলে চিত্রা’র একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমন বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে।
ঐ ছোট্ট একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল বলে আকাশ ভরা জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি- বাইরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য দ্যুলোক ভূলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি না।
অহং আমাদের সেইরকম জিনিস- অত্যন্ত কাছে এই জিনিসটা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চার দিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে যে অনন্ত আকাশ ভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে- এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুর্হূতে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন।
সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে আনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি- সে যে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম।
এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন- নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।
[৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ]
বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।
তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।
আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।
[১৩১৯ বঙ্গাব্দ]
বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল।
বৌদ্ধযুগে সেই সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্ম বন্যায় ভাঙিয়াছিল- শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল।
তারপরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ।
এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না।
আভ্যন্তরিন নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়- যাহা কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।
যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোরূপ পরিচয় হাওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।
ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে।
মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।
এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।
এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।
এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি।
দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ইহারাই আর সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।
সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।
[১৩২৬ বঙ্গাব্দ]
একদিন বুদ্ধ বললেন, আমি সমস্ত মানুষের দু:খ দূর করব। দু:খ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।
ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে!
[১৭ ভাদ্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দ]
ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।
চীনে গেলাম। দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে।
এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি; এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দু:খ দিয়ে নয়, নিজে দু;খ স্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্যভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে।
এই সত্যের কথা বিদেশী পরিটিকসের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।
জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।
সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপচিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে।
এই কারণেই সেই সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই সব জায়গাতেই।
[শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ]
বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাত কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে; তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত।
প্রাণীজগতের নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেটই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীয় শক্তিতে আত্মত্যাগ।
জীব জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালী পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের পরে আঘাত লাগছে।
সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমানে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়িরে গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড় বিস্ময় লেগেছিল।
বুদ্ধই যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতক কথা লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই মেষ গিয়ে পৌচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে।
এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এত বড় মন্দিরভিত্তিক গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।
[২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭/১৩৩৪]
বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রী স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে- একেই বলে ব্রহ্মবিহার।
এত বড় উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোহহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।
অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে- যিনি বিদ্বান্ তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দু:সাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদু: পরমেষ্ঠিনম্- যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই।
সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন-
মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে
এমম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াবাব জন্মাবে। মাথা গনে বলব না, কজন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।
মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।
[১৩৩৯ বঙ্গাব্দ]
……………………………….
ভাববাদ-আধ্যাত্মবাদ-সাধুগুরু নিয়ে লিখুন ভবঘুরেকথা.কম-এ
লেখা পাঠিয়ে দিন- voboghurekotha@gmail.com
……………………………….
……………………
আরও পড়ুন-
বুদ্ধদেব
ভগবান্ বুদ্ধ
বুদ্ধদেব প্রসঙ্গ
ব্রহ্মবিহার