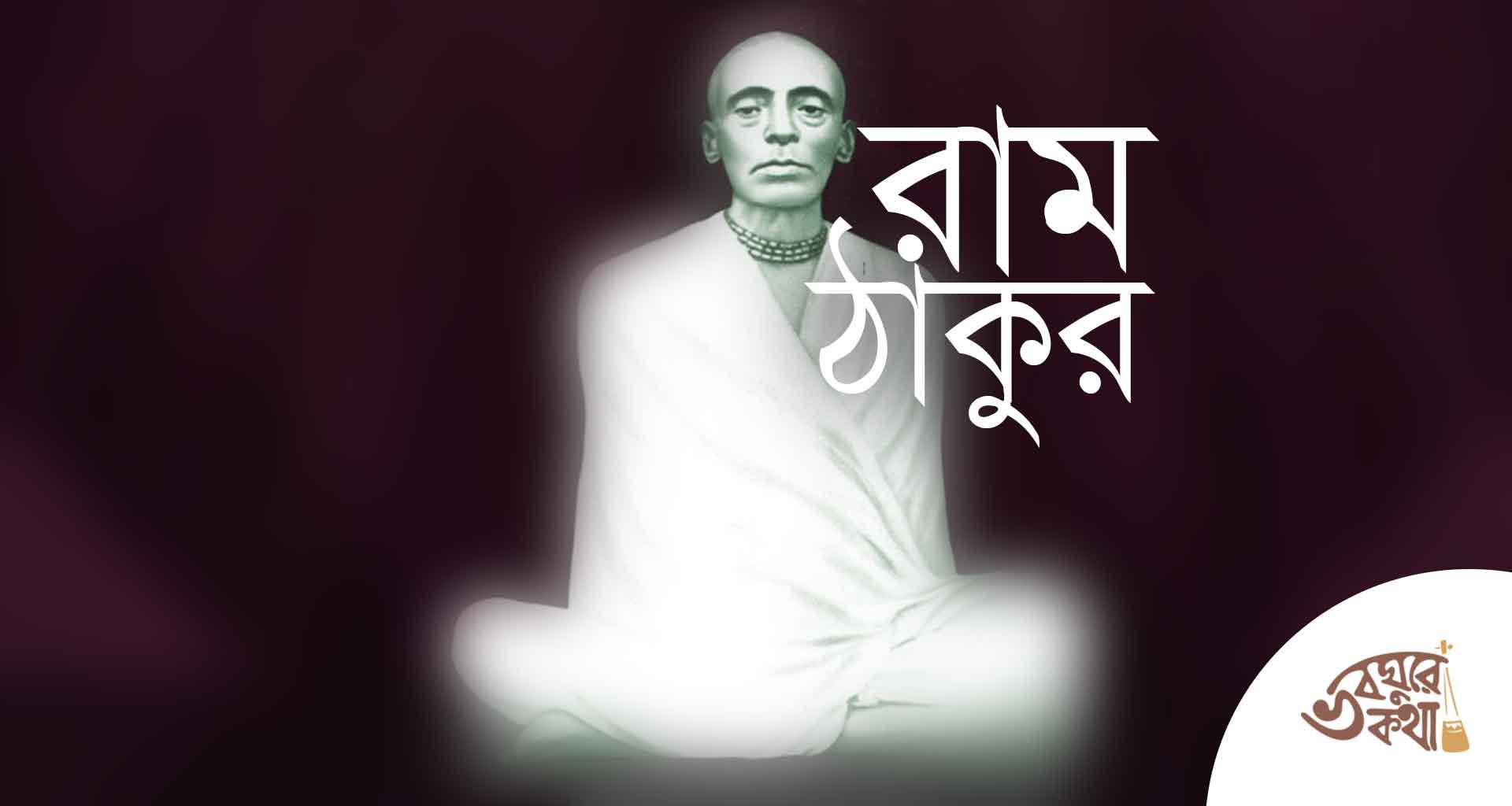১৯২৪ সালের পর থেকেই ঠাকুরের শিষ্য-সংখ্যা বাড়তে থাকে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় প্রতিটি শহরে ও গাঁয়ে অসংখ্য নরনারী দীক্ষাগ্রহণ করে ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ভক্তরা সকলেই আক্ষেপ করেন, ঠাকুরকে এক জায়গায় তারা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেন না। ঠাকুরের পবিত্র সান্নিধ্যে হতে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা, কারণ ঠাকুর এক জায়গায় কোথাও স্থায়ী হচ্ছেন না। এজন্য ঠাকুরের মনোমত কোন জায়গায় একটি আশ্রম গড়ে তোলার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করতে লাগলেন।
একবার শোনা গেল পুরীতে অনেক জমি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই আশ্রম হবে। পরে ঢাকা শহরের একপ্রান্তে কিছু ভাল জমি দেখে ঠাকুরের কাছে প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত হয় না। ঠাকুরের মত না পাওয়ার জন্য আশ্রম নির্মাণের কাজ শুরু হলো না। অবশেষে মত মিলল ঠাকুরের। অগণিত ভক্তের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। তাদের বহুদিনের মনের সাধ পূরণের পথে আর কোনো বাঁধা রইল না।
চট্টগ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়তলী রেল স্টেশনের কাছে ছোট্ট একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের উপরে কিছু জায়গা পাওয়া গেছে। এবার সহজেই ঠাকুরের সম্মতি মিলল। আশ্রম তৈরি হবে সেই পাহাড়ের উপরে। শেষ জীবনে সেখানে বিশ্রাম করবেন ঠাকুর। তাঁর ভ্রাম্যমাণ পরিব্রাজক জীবনের অবসান হবে। দূর-দূরান্ত হতে অগণিত ভক্ত এসে ঠাকুরের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হবে।
কাজ শুরু হয়ে গেল। ভক্তদের বিরামহীন তৎপরতায় ও অক্লান্ত চেষ্টায় নির্মাণকার্য খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সংবাদ ঘোষণা করা হলো, ১৩৩৭ সালের ১৫ই ফাল্গুন আশ্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করবেন ঠাকুর। এই উপলক্ষে তিনদিন ধরে উৎসব হবে। এ কথা যথাসময়ে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দূরদূরান্ত হতে অসংখ্য মানুষ পায়ে হেঁটে, স্টীমারে, ট্রেনে করে আশ্রমে এসে উপস্থিত হতে লাগল।
সেই বছরেই আশ্রমে ভক্তরা খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজো করে। শোনা গেল, পূজোর সময় ঠাকুর আসবেন সেই পাহাড়তলীর আশ্রমে। সেকথা শুনে দলে দলে ভক্তরা আসতে লাগল ঠাকুরকে দর্শন করার আশায়। কিন্তু একে একে পূজোর সব দিন কটি’ই চলে গেল কিন্তু ঠাকুর এলেন না। একখানি চিঠি লিখে জানালেন স্থূল দেহে ঐ আশ্রমে প্রবেশের অধিকার আমার থাকল না!
যথাসময়ে ঠাকুরও এসে উপস্থিত হলেন। ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। সকলেই ভাবতে লাগল, ঠাকুর এবার থেকে স্থায়ী হলেন, এই মনোরম স্বাস্থ্যকর জায়গায় অবস্থিত এমন সুদৃশ্য আশ্রমভবন ছেড়ে ঠাকুর আর কোথাও যাবেন না। তিনদিন ধরে সমানে চলল উৎসব। একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে ঠাকুরকে বিগ্রহ দেবতার মত ভক্তি সহকারে বসিয়ে ভক্তরা তাঁকে ঘিরে আনন্দ করতে লাগল।
কিন্তু আশ্চর্য! তিনদিন গত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর উঠে পড়লেন। সকলের কাছে বিনীতভাবে বললেন, আমি তাহলে আসি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক কাপড়ে ও চাদরে পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নেমে চললেন ঠাকুর। তারপর শহরের পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মানুষের মানুষের অরণ্যে। বজ্রাহতের মত এক স্তব্ধ বিস্ময়ে ও বেদনায় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উপস্থিত ভক্তগণ।
ঠাকুরের পথপানে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন তারা। সব সাধু-সন্ন্যাসীরাই আশ্রম জীবনযাপন করেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই একটি করে ডেরা আছে, কিছু কিছু সঞ্চয় আছে। এমন কি যারা পরিব্রাজকের বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান তাঁদেরও কন্থা, করঙ্গ প্রভৃতি কিছু কিছু সম্বল থাকে সঙ্গে। কিন্তু ঠাকুরের তাও নেই।
এক বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের চড়া সুরে এমনভাবে এই মহান পুরুষের জীবনের তারটি বাঁধা, খাওয়া পরাজাতীয় কোন ভোগবাসনা কখনো চঞ্চলিত করতে পারে না তাঁর নিত্যমুক্ত চিত্তকে। ভক্তি ভালোবাসার কোন নিবিড়তা বিন্দুমাত্র আসক্ত করে তুলতে পারে না চির-উদাসীন মনকে, শান্ত সুন্দর কোন ঘরের সুখস্রাবী সীমা আবদ্ধ করে রাখতে পারে না তাঁর দেহকে।
সেই বছরেই আশ্রমে ভক্তরা খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজো করে। শোনা গেল, পূজোর সময় ঠাকুর আসবেন সেই পাহাড়তলীর আশ্রমে। সেকথা শুনে দলে দলে ভক্তরা আসতে লাগল ঠাকুরকে দর্শন করার আশায়। কিন্তু একে একে পূজোর সব দিন কটি’ই চলে গেল কিন্তু ঠাকুর এলেন না। একখানি চিঠি লিখে জানালেন স্থূল দেহে ঐ আশ্রমে প্রবেশের অধিকার আমার থাকল না!
গুরুদেব আশ্রমের ভার গ্রহণ করলেন। ঠাকুরের গুরুদেব কে এবং কেনই বা তিনি একথা লিখলেন তার অর্থ কেউ বুঝতে না পারলেও একটা বিষয় এর থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যেতে পারে। ঠাকুর এখানে গুরুদেব বলতে ঈশ্বরকে বুঝিয়েছেন।
আর তাঁর জন্য বিশেষ করে বহু অর্থ ও উদ্যমব্যয়ে নির্মিত এই সুদৃশ্য আশ্রম ভবনটিতে একাধিকবার আসা যাওয়া করলে পাছে তার প্রতি আসক্তি জাগে অন্তরে, এই ভয়েই ঠাকুর আর সেখানে আসতে চান না ; তাই ঈশ্বরকে অর্পণ করেছেন সে আশ্রমের সব ভার।
প্রারব্ধ কর্মের ফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে। ঠাকুর বলতেন, যাবতীয় রোগ, শোক, দুঃখ-দুর্দশা প্রারব্ধ কর্মের ফল। এই কর্মফল ভোগ পূর্ণ না হলে কেউ ঈশ্বরকে পেতে পারে না; চিরশান্তি লাভ করতে পারে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বলেছেন-
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়।
তুমি আমাতেই মনপ্রাণ স্থির রেখে আমাতেই সমস্ত বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। তার ফলে এই দেহের শেষে অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ শেষ হয়ে গেলে তুমি আমাকেই পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেহধারণ মানেই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ এবং শত সাধনাতেও এই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ এড়ানো যায় না। এই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ শেষ না হলে কোন সাধক ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন না।
এজন্য ঠাকুর যখন কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হতেন তখন শিষ্যদের তাঁর জন্য কোনো ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে বলতেন না। অথচ বহু দূর দূরান্ত হতে যে সব ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ তাঁর কাছে প্রতিকারের জন্য আসত তাদের রোগমুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তিনি। তবে কোনো রোগীকে দেখে যদি বুঝতেন, তার মৃত্যু অবধারিত, তাহলে কোন কথা বলতেন না। বলতেন প্রাক্তনের ফল ভোগ করতেই হবে।
ঠাকুর একবার উত্তর প্রদেশের কোন একটি ধনী লোকের একমাত্র ছেলের কঠিন বাতরোগ নিজের দেহে গ্রহণ করে সেই ছেলেটিকে চিরকালের জন্য রোগমুক্ত করেন। সেই থেকে মাঝে মাঝে এই কঠিন বাতরোগের অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতেন। তবু তার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করতেন না।
একবার চাঁদপুরে থাকার সময় কঠিন রক্ত আমাশয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন ঠাকুর। ভক্তরা বহু চেষ্টাতেও আরোগ্য করতে পারলেন না তাঁকে। অবশেষে ঠাকুর কলকাতায় চলে এলেন এবং তাঁর রোগ সেরে গেল। ঠাকুর বলতেন প্রাক্তনের খণ্ডন হলেই রোগ সারবে।
সেকালে মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান খুব প্রবল ছিল। জাতিভেদ বর্ণভেদের জন্য বিরোধ লেগেই ছিল। ঠাকুর এতে অত্যন্ত ব্যথা পেতেন। একবার ভক্তদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য একটি চমৎকার ঘটনার অবতারণা করেন ঠাকুর। ঠাকুর উপস্থিত ভক্তদের বললেন, আমার রাহুর দশা চলছে। ভক্তরা সবাই জানত, ঠাকুর ভালো কুষ্ঠী বিচার করতে পারেন।
দুস্থ ও আর্তের প্রতি দয়ার অন্ত ছিল না ঠাকুরের। কারো অকালমৃত্যু রোধ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। একবার ঠাকুরের ভাইপোর ছেলে সন্তোষের কঠিন বসন্ত রোগ হয়। বাঁচবার কোন আশা ছিল না। সমস্ত দেহটি ফুলে গিয়েছিল, চোখগুলি ঢেকে গিয়েছিল। কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। তবু বেঁচে উঠল ছেলেটি। ভাল হয়ে উঠে সে বলল, বাহ্যজ্ঞান না থাকলেও সে অনুভব করেছে, রোজ ঠাকুর এসে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলোতেন।
ঠাকুর এইভাবে সুক্ষ্মদেহে উপস্থিত হয়ে বহু রোগীর সেবা করতেন। কোন্ রোগীর মৃত্যু অবধারিত তাও তাকে দেখে বুঝতে পারতেন। একবার তাঁর জন্মভূমি ডিঙ্গামানিকে একটি মেয়ে কঠিন অসুখে ভুগতে থাকে। ঠাকুর সেখানে গিয়ে নিজের হাতে সেবা করতে থাকেন।
একদিন শেষ রাতের দিকে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। কিন্তু প্রাণ কিছুতেই বার হয় না। ঠাকুর তখন একবার স্থির হয়ে বসে ধ্যানস্থ হলেন। তারপর উঠে তাঁর সহকারী সতীনাথবাবুকে বললেন, চল, আমরা সরে যাই। আমরা বিছানায় রয়েছি বলে আত্মা ওর বেরিয়ে চলে যেতে পারছে না। অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা।
এই ঘটনা থেকে ভক্তরা বুঝতে পারল, ঠাকুরের জাতিবর্ণের কোন বিচার নেই। তিনি সদাসর্বদা অচণ্ডালে কোল দিতে প্রস্তুত। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোন লোককে তিনি দীক্ষা দিতেন, অনেক মুসলমান তাঁর ভক্ত ছিল। বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে দীক্ষা দিতেন ঠাকুর। কাউকে বৈষ্ণব মতে, কাউকে শাক্ত মতে, আবার কাউকে বৈদান্তিক মতে ওঙ্কার মন্ত্র জপ করতে দিতেন। তবে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে হলে দীক্ষার্থীকে ধৈর্য ধরতে হত।
ঠাকুর বিছানা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করল মেয়েটি। ঠাকুর বলতেন, অবধারিত মৃত্যু হচ্ছে প্রাক্তন। এই অবধারিত বা বিধিনির্দিষ্ট মৃত্যুকে রোধ করবার চেষ্টা করতে নেই।
ঠাকুর ছিলেন বৈষ্ণবীয় দীনতার মূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন তৃণের চেয়েও সুনীচ, আবার কুসুমের চেয়েও সুকোমল। কিন্তু আপন স্বভাবধর্মে তিনি ছিলেন অচল এবং অটল। কেউ তাঁর ইচ্ছা বা নীতির বিরুদ্ধে কিছু করাতে পারত না। শত অনুনয় বিনয়েও এতটুকু স্বভাবধর্মচ্যুত হতেন না। সকল মানুষকেই ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করতেন।
সেকালে মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান খুব প্রবল ছিল। জাতিভেদ বর্ণভেদের জন্য বিরোধ লেগেই ছিল। ঠাকুর এতে অত্যন্ত ব্যথা পেতেন। একবার ভক্তদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য একটি চমৎকার ঘটনার অবতারণা করেন ঠাকুর। ঠাকুর উপস্থিত ভক্তদের বললেন, আমার রাহুর দশা চলছে। ভক্তরা সবাই জানত, ঠাকুর ভালো কুষ্ঠী বিচার করতে পারেন।
কোন ভক্তের বাড়িতে গিয়ে যদি দেখতেন কারো ছেলে হয়েছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই নবজাতকের কুষ্ঠী তৈরি করতে শুরু করতেন। তাই তাঁর কথা শুনে ভক্তরা ভাবতে লাগল ঠাকুরের রাহুর দশা কি করে কাটানো যায়। ঠাকুর বললেন, একটা উপায় আছে। কোন এক নমঃশূদ্র লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাতাতে হবে।
তখন ১৯৩৬ সাল। সেকালে নমঃশূদ্রদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা নীচজাত বলে ঘৃণা করত। ঠাকুরের কথা শুনে সকলে শহরের চারিদিকে খোঁজ করতে লাগলেন। অবশেষে হরিদাস আচার্য মশাই ঠাকুরের সেই ভাবী বন্ধুর সন্ধান পেলেন। বন্ধুটি বর্ণে নমঃশূদ্র এবং বয়সে বৃদ্ধ।
সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। লাঠি ধরে চলেন। লোকটিকে বুঝিয়ে একদিন সকালবেলা ঠাকুরের কাছে আনা হতেই ঠাকুর বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাকে পাশে বসিয়ে বললেন, আপনি আমার বন্ধু ; আপনি আমায় মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।
লোকটি সেকথা বুঝতে পারল না। তা না পারলেও ঠাকুর তাকে ছাড়লেন না। তাকে নতুন কাপড় চাদর পরিয়ে যত্ন করে খাওয়ানো হলো। তারপর বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো। বিশ্রামের পর বিকেলে তাকে বিদায় দেওয়া হলো। পরে লোকটিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, সবই ঠাকুরের লীলা ; আমি কিছুই জানি না।
এই ঘটনা থেকে ভক্তরা বুঝতে পারল, ঠাকুরের জাতিবর্ণের কোন বিচার নেই। তিনি সদাসর্বদা অচণ্ডালে কোল দিতে প্রস্তুত। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোন লোককে তিনি দীক্ষা দিতেন, অনেক মুসলমান তাঁর ভক্ত ছিল। বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে দীক্ষা দিতেন ঠাকুর। কাউকে বৈষ্ণব মতে, কাউকে শাক্ত মতে, আবার কাউকে বৈদান্তিক মতে ওঙ্কার মন্ত্র জপ করতে দিতেন। তবে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে হলে দীক্ষার্থীকে ধৈর্য ধরতে হত।
কেউ যদি বলত, ঠাকুর আমায় দয়া করে দীক্ষা দিন, তাহলে ঠাকুর বলতেন, আমি দীক্ষা দেব কি, আমার নিজেরই দীক্ষা হলো না। আমি দয়া করবার কে? আবার কাউকে বলতেন, এখানে আপনার পাওনা নেই। আবার কাউকে বলতেন, সময় হলেই পাবেন। দীক্ষাপ্রার্থীকে কড়াভাবে লক্ষ্য করতেন এবং হাত গুণে কী যেন আওড়াতেন আপন মনে।
অনেকে বলত, ঠাকুর সত্তা নির্ণয় করছেন লোকটির। অর্থাৎ সকলের স্বভাব তো সমান নয়। আর এক মন্ত্র সকলের পক্ষে ফলপ্রদ নয়। তাই ক্ষেত্র বুঝে যেমন বীজ বপন করতে হয় তেমনি লোক বুঝে মন্ত্রদীক্ষা দান করতেন ঠাকুর। দীক্ষাকালে নামমন্ত্র শুধু মুখে উচ্চারণ করতেন না, কাগজে লিখে তার ব্যাখ্যা করে ভিতরকার তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিতেন।
অনেক সময় অনেক দীক্ষার্থী বারবার ঠাকুরের কাছে আবেদন নিবেদন করেও দীক্ষা পেত না। ঠাকুর হয়ত তাকে বললেন, হবে। পরে দেখা গেল, সে স্বপ্নাবস্থায় নাম পেয়ে গেছে। তবু তাতে তৃপ্ত হত না তার মন। তাই ঠাকুরের কাছে ছুটে যেত। ঠাকুর তার সামনে নিজে মুখে সেই নাম উচ্চারণ করলে পর তবে সে সন্তুষ্ট হত।
ঠাকুর বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন দীক্ষা দিতে পারতেন, তার অর্থ এই যে, তিনি বিভিন্ন মার্গের সাধন পদ্ধতিতে সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজেকে কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবী করতেন না। একবার কুম্ভমেলায় এক সাধু সমাবেশে ঠাকুর যোগদান করেছিলেন।
কারণ ঠাকুরের কোন আমিত্ববোধ ছিল না। অবিচলিতচিত্ততার মূল ভিত্তি হলো অহংবোধের নিঃশেষিত বিলুপ্তি। আমি আছি, আমি জানি, আমি কাজ করি বা নিজেকে প্রকাশ করি। এ সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না ঠাকুরের। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বাভিমান বা আমিত্ববোধ ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বাত্ববোধে বিলীন হয়ে গিয়েছিল কখন, তা তিনি নিজেই জানতে পারেননি।
এই সমাবেশে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু এসে সমবেত হন। ঠাকুর দীনহীনভাবে একধারে চুপচাপ বসেছিলেন। তিনি কোন প্রচার চাইতেন না। তাঁর কোন গেরুয়া কাপড় বা মাথায় জটা ছিল না। মুণ্ডিত মস্তক, গলায় তুলসী কাঠের মালা, পরনে পাড়হীন একখানি ধুতি আর গায়ে একখানি সাদা নিমা বা চাদর।
ঠাকুরকে দেখে সাধারণতঃ বৈষ্ণব সাধক বলেই মনে হত। তবু সমাবেশের একজন সাধু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের?” ঠাকুর সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে আমি মানব সম্প্রদায়ের।”
ঠাকুরের বক্তব্যের অর্থ এই যে, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়চেতনা বাঁধা সৃষ্টি করে প্রকৃত সাধনার পথে। সমস্ত সাধনার মূল লক্ষ্য হলো ঈশ্বর লাভ। যে ঈশ্বরের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে অংশীভূত হয়ে বিরাজ করছে, তা কখনো বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।
সাধনমার্গ যাই হোক না কেন, সাধকের নিষ্ঠা থাকা চাই। তা না হলে সব বৃথা। একদিন দুর্গাপূজার কথা উঠলে ভক্তদের কাছে ঠাকুর হঠাৎ বলে ওঠেন, দূর্গোৎসব না করাই ভাল। ভক্তরা ঠাকুরের এ কথার অর্থ জানতে চাইলে ঠাকুর বলেন, দেবীর আবাহন করলে গুরুদায়িত্বের কথা এসে পড়ে। দেবীর আগমনকাল থেকে বিসর্জন পর্যন্ত দেবীর পূজার যাতে কোন ত্রুটি না হয় এবং দেবী যাতে ঠিকমত তৃপ্ত হন তার জন্য শাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা করা চাই। তা না হলে পূজার কোন অর্থ হয় না।
বিষ্ ধাতু থেকে বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি। বিষ্ ধাতুর অর্থ হলো ব্যাপ্ত হওয়া। বিশ্বচরাচরের সর্বভূতে ও সর্ববস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন বলেই তিনি বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর যাঁরা ভক্ত, তাঁদের বলে বৈষ্ণব। ঠাকুর ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব। কারণ তাঁর আত্মা একই সঙ্গে বিশ্বের সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকত সতত। সর্বজীবের সঙ্গে সব সময় একাত্মতা বোধ করতেন তিনি।
জীবনে কোন বন্ধন বা সংকীর্ণতাকে স্বীকার করেননি কখনো। তিনি ছিলেন বেদান্তবর্ণিত ব্রহ্মস্বরূপসম্পন্ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এক পরম পুরুষ। যাঁকে কোন ঘরের বন্ধন কোন দিন বাঁধতে পারেনি; কোনো বিশেষ বস্তু বা জীবের প্রতি কোন মায়ামমতা যাঁর ব্যাপ্তিবোধকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি আত্মকর্তৃত্বাভিমান বা কর্মফলাসক্তি শক্তি যাঁর চিত্তকে কখনো আচ্ছন্ন বা কলুষিত করতে পারেনি।
সত্যিই ঠাকুর ছিলেন এক আশ্চর্য পুরুষ। সাধারণতঃ জীবনে অবস্থার তারতম্য বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত মনের ভাবের পরিবর্তন হয়। একথা শুধু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই খাটে না ; সাধকদের জীবনেও এই ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঠাকুর ছিলেন সব অবস্থাতেই সমান। শীতে ও গ্রীষ্মে তিনি একই পোশাক পরতেন, সেই একখানি কাপড় আর একটি খদ্দরের চাদর। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হতে কেউ কখনো দেখেনি তাঁকে। কোন ঘটনাতে বিশেষভাবে দুঃখিত বা আনন্দিত হতে দেখা যায়নি তাঁকে।
কারণ ঠাকুরের কোন আমিত্ববোধ ছিল না। অবিচলিতচিত্ততার মূল ভিত্তি হলো অহংবোধের নিঃশেষিত বিলুপ্তি। আমি আছি, আমি জানি, আমি কাজ করি বা নিজেকে প্রকাশ করি। এ সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না ঠাকুরের। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বাভিমান বা আমিত্ববোধ ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বাত্ববোধে বিলীন হয়ে গিয়েছিল কখন, তা তিনি নিজেই জানতে পারেননি।
গীতায় ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অভ্যাসযোগ অর্থাৎ বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ ও চিন্তনের দ্বারা তাঁকে পাবার চেষ্টার থেকে জ্ঞান বড়। জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান বড়। আবার ধ্যানের চেয়ে কর্মফল ত্যাগ করা ভাল। এই কর্মফলাসক্তিহীনতা জ্ঞানকে দান করে পরিপূর্ণতা। ভক্তিকে করে তোলে পরিশুদ্ধ। ঠাকুর ছিলেন পরম জ্ঞানী। কারণ তিনি জানতেন, তিনি কিছুই জানেন না।
ঠাকুর ছিলেন পরম কর্মযোগী। কারণ তিনি মনে করতেন, তিনি কিছুই করছেন না। ঠাকুর ছিলেন পরম ভক্ত। কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত। ঠাকুর ছিলেন সাকার উপাসক। তাঁর প্রাণের হরির মধ্যেই তিনি উপনিষদের অখিল রসামৃত পুরুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরম হরিভক্ত।
অন্তরে যাঁর ধ্যান করতেন, মুখে করতেন তাঁর নামকীর্তন আর হাত দিয়ে করতেন তাঁরই পূজা। এইভাবে কায়িক মানসিক ও বাচিক সমস্ত কর্মোদ্যমের মাধ্যমে ঠাকুর নিজের জীবনকে এক মহাপূজার নৈবেদ্যরূপে সমর্পণ করেছিলেন শ্রীহরির চরণে।
(চলবে…)
………………………………………..
ভারতের সাধক ও সাধিকা
লেখক : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
………………….
পুনপ্রচারে বিনীত: প্রণয় সেন
……………………………….
ভাববাদ-আধ্যাত্মবাদ-সাধুগুরু নিয়ে লিখুন ভবঘুরেকথা.কম-এ
লেখা পাঠিয়ে দিন- voboghurekotha@gmail.com
……………………………….
………………….
আরও পড়ুন-
স্বামী অড়গড়ানন্দজী
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
শিরডি সাই বাবা
পণ্ডিত মিশ্রীলাল মিশ্র
নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার অন্যতম পার্ষদ ছিলেন রায় রামানন্দ
ভক্তজ্ঞানী ধর্মপ্রচারক দার্শনিক রামানুজ
সাধক ভোলানন্দ গিরি
ভক্ত লালাবাবু
লাটু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন
পরিব্রাজকাচার্য্যবর শ্রীশ্রীমৎ দূর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব
আর্যভট্ট কাহিনী – এক অজানা কথা
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
কঠিয়াবাবা রামদাস
সাধু নাগ মহাশয়
লঘিমাসিদ্ধ সাধু’র কথা
ঋষি অরবিন্দ’র কথা
অরবিন্দ ঘোষ
মহাত্মাজির পুণ্যব্রত
দুই দেহধারী সাধু
যুগজাগরণে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ
শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর
বাচস্পতি অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে
মুসলমানে রহিম বলে হিন্দু পড়ে রামনাম
শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব : প্রথম খণ্ড
শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব: দ্বিতীয় খণ্ড
শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব : অন্তিম খণ্ড
মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ
শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর
শ্রীশ্রী ঠাকুর সত্যানন্দদেব
মহাতাপস বালানন্দ ব্রহ্মচারী: এক
মহাতাপস বালানন্দ ব্রহ্মচারী: দুই
মহাতাপস বালানন্দ ব্রহ্মচারী: তিন
সাধক তুকারাম
সাধক তুলসীদাস: এক
সাধক তুলসীদাস: দুই
সাধক তুলসীদাস: তিন
শ্রীশ্রী মোহনানন্দ স্বামী: এক
শ্রীশ্রী মোহনানন্দ স্বামী: দুই
শ্রীশ্রী মোহনানন্দ স্বামী: তিন